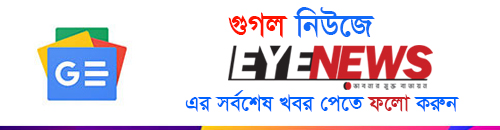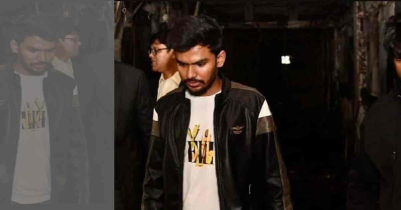প্রকাশিত: ১১:৩৮, ২৮ মে ২০১৯
আপডেট: ১২:০৪, ২৮ মে ২০১৯
আপডেট: ১২:০৪, ২৮ মে ২০১৯
রাজা রামমোহন রায় ও সতীদাহ প্রথা
মণিমেখলা মাইতি: ১৮১৭-র শেষ দিকে শিব বাজারের কবিরাজ মারা গেলে তার দুই স্ত্রী সতী হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। বড় বউ বছর তেইশের যুবতী। ছোট বউ সবে সতেরো। পুলিশে খবর গেল। চব্বিশ পরগণার স্হানীয় পুলিশ ছুটে এসে বোঝাতে চেষ্টা করল। কিছু লাভ হল না। কালীঘাটের গঙ্গাতীরে সহমরণের ব্যবস্থা হল। সতীদাহ হবে শুনে আশেপাশের এলাকায় কী হুড়োহুড়ি! মেয়েরা ছুটে এল সতীর পায়ের ধুলো নেবে। এ ধুলো যে নেয় সে পুণ্যবতী।
রামমোহন রায় তখন মানিকতলায়। খবর পেয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মানিকতলা থেকে কালীঘাট যাওয়া সোজা নয়। দীর্ঘ পথ। তাছাড়া চৌরঙ্গীর জঙ্গল আছে। সরু পথ। সে পথে দিনের বেলা বেহারারা যেতে ভয় পায়। রামমোহন ছুটছেন। রামমোহনকে দেখে স্হানীয় জনতার মধ্যে আলোড়ন পড়ে গেল। তিনি সটান শ্মশানে গিয়ে মেয়ে দুটিকে বোঝালেন। সফল হলেন না। মেয়ে দুটি অনড়, তারা সতী হবেই। সতী হলে কত পুণ্য! অঙ্গিরা মুণি বিধান দিয়ে গেছেন, যে স্ত্রী ঐ পতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে বশিষ্টর স্ত্রী অরুন্ধতীর সমান হয়ে স্বর্গারোহণ করে। আর যে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যায় সে মানুষের দেহে যত লোম আছে অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গবাস করে। সাপ সংগ্রহকারী যেমন নিজের শক্তির বলে গর্ত থেকে সাপ উদ্ধার করে তেমনই স্বামী মারা গেলে ওইরকম ক্ষমতার দ্বারা ঐ স্ত্রী স্বামীকে স্বর্গে নিয়ে সুখভোগ করে। আর যে স্ত্রী সহমৃতা হয় সে তিন কুলকে পবিত্র করে। পুণ্যলাভের এমন সুবর্ণসুযোগ ছাড়া চলে!
অগত্যা রামমোহন নির্দেশ দিলেন মেয়েদের চিতায় বেঁধে তার উপর ডালপালা চাপিয়ে আগুন ধরালে চলবে না। চিতায় আগে অগ্নিসংযোগ হবে। তারপর মেয়ে দুটি স্বেচ্ছায় উঠবে। কোনও জবরদস্তি চলবে না। প্রস্তাবটি উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের ঠিক পছন্দ হল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা রাজি হল। রামমোহনের মনে আশা যদি মেয়ে দুটো শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়ে বেঁকে বসে। কিন্তু রামমোহন অবাক হয়ে দেখলেন বড় বউটি নির্বিকার চিত্তে উঠে গেল চিতায়। তার দেখাদেখি ছোট বউ। চারিদিকে উল্লাস, ঢাকঢোলের শব্দ। মাথা নীচু করে মানিকতলা ফিরে এলেন রামমোহন রায়।
ব্যাপক হারে তখন বাংলায় সতীদাহ প্রথা চলছে। Parliamentary Papers(HOC),1825,Vol-XXIV এ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলা বিভাগে ১৮১৫ সালে সতী হয়েছে ৩৭৮ জন (তার মধ্যে কলকাতা বিভাগে ২৫৩ জন), ১৮১৬ সালে সতী হয়েছে ৪৪২ জন (কলকাতা বিভাগে ২৮৯ জন); ১৮১৭ সালে সতীর সংখ্যা ৭০৭ জন (কলকাতায় ৪৪২ জন); ১৮১৮ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে সতীর সংখ্যা ৮৩৯ জন (কলকাতা বিভাগে তার মধ্যে ৫৪৪ জন); ১৮১৯ সালে বাংলায় সতীর সংখ্যা ৬৫০ (কলকাতায় ৩৭০ জন); ১৮২০ সালে সর্বমোট ৫৯৭ জনের মধ্যে কলকাতায় সতীর সংখ্যা ৩৭০। তখন তো বাংলা প্রেসিডেন্সিতে কলকাতা বিভাগ ছাড়াও ঢাকা বিভাগ, মুর্শিদাবাদ বিভাগ, পাটনা বিভাগ, বেনারস বিভাগ ও বেরিলি বিভাগ ছিল। কিন্তু সতীদাহ সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল কলকাতা বিভাগে। পার্লামেন্টের পেপারের তথ্য অনুযায়ী সতীদাহে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বেনারসকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে কলকাতা বিভাগ।
আবার কলকাতা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সতীদাহ হয়েছে বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া, কলকাতার উপকণ্ঠ ও জঙ্গলমহলে। ১৮১৯ সালের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সতীদাহ’র সংখ্যা– বর্ধমান: ৭৫, হুগলি: ১১৫, নদিয়া: ৪৭, কলকাতা উপকণ্ঠ: ৫২, জঙ্গলমহল: ৩১, কটক/পুরী: ৩৩, যশোর: ১৬, মেদিনীপুর: ১৩ ও ২৪ পরগণা: ৩৯। চুঁচুড়ার কোনও পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। হাউস অফ কমন্সের নির্দেশে এই পরিসংখ্যান 1825 সালের ১ জুলাই লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়।
 বাংলায় যখন সতীদাহ প্রথার এমন রমরমা, তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সতীদাহর সংখ্যা নগণ্য, হাতে গোনা। চব্বিশ পরগণার আড়িয়াদহ, নৈহাটি, বৈদ্যবাটি, হরিপাল, সালকিয়া, চিৎপুর, কালনা-কাটোয়া, বিষ্ণুপুরে প্রায়ই সতীর চিতা জ্বলত। কেরীর তালিকা অনুযায়ী ১৮০৩ সালে সতী হয় ২৭৫ জন। ১৮০৪ সালে ছয় মাসে ১১৬ জন। অদ্ভুত ব্যাপার শিক্ষার হার যেখানে একটু বেশি সেখানেই সতীদাহর ঘটনা বেশি। ১৮২৩–এ ৫৭৫ জন সতী হয়। ১৮২৬–এ ৬৩৯ জনের মধ্যে কলকাতায় ৩৬৮ জন।
খ্রিস্টপূর্বকাল থেকেই ভারতে সতীদাহ’র মতো ঘটনা ঘটে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭–এ আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় পাঞ্জাবে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ‘রাজতরঙ্গিনী’তে আছে সতীর ঘটনা। বরাহমিহির সতীর গুণগান গেয়েছেন। মঙ্গলকাব্যে আছে সতীর উল্লেখ। মুলতান থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে ইবন বতুতা আমঝারিতে তিনজন মেয়েকে সতী হতে দেখে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আবার বার্নিয়েরের মতো কেউ কেউ সতী হওয়া থেকে কোনও কোনও মেয়েকে রক্ষা করেছেন। তাঁর নজর এড়ায়নি যে প্রধানত ব্রাহ্মণরা হিন্দু মেয়েদের সতী হতে উৎসাহ দিত। সবাই স্বেচ্ছায় সতী হত না। কিন্তু একটা বিধবা মেয়ের আজীবন ভরণপোষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অথবা তার সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য জোর করে তাকে চিতায় উঠতে বাধ্য করা হত।
স্বপন বসুর “বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস” বইতে পাই যে মেয়েরা সতী হলে কোনও কোনও ধনী পরিবার থেকে তখনকার সময় দুইশত টাকা অবধি সাম্মানিক জুটত। এই অর্থের লোভে ব্রাহ্মণরা মেয়েদের সতী হতে উৎসাহ দিত। স্বপন বসুর ‘সতী’ নামক বইতেই দেখি একটি অল্পবয়সি মেয়ের স্বামী মারা যেতে সে সতী হবে বলে মনস্থির করল। আত্মীয়স্বজন বেজায় খুশি। চারিদিকে সাজো সাজো রব। চিতার আগুন জ্বলে উঠতেই মেয়েটির কাকা মেয়েটিকে ধরে চিতায় তুলে দিল। আগুনে ঝলসে মেয়েটি বাঁচবার জন্য চিতা থেকে লাফ দিল। শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি। চিতা থেকে পালালে চলবে না। সংকল্প যখন করেছে তাকে সহমরণে যেতেই হবে। আধপোড়া মেয়েটা প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে একটা ঝোপের পিছনে আশ্রয় নিল। তার কাকা কিন্তু লোকজন সঙ্গে এনে তাকে ঠিক খুঁজে বের করে আবার জবরদস্তি করে চিতায় তুলে দিল। পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে পুরো পরিবারের মান সম্মান বাড়িয়ে দিয়ে গেল মেয়েটি।
আর একটি খুব অদ্ভুত গল্প পড়েছিলাম। একটি লোকের তিন বউ। প্রথমজনকে বিয়ে করে একদিনও সংসার করেননি। দ্বিতীয় স্ত্রী মানসিক বিকারগ্রস্ত। তাই তিনি তৃতীয় একজনকে বিয়ে করে তার সঙ্গে থাকতেন। তিনি মারা গেলে কে সতী হবে? ছোট বউ আর মানসিক বিকারগ্রস্ত বউটি বলল তারা সতী হবে। কিন্তু চিতার অমন ভয়াল রূপ দেখে ছোট বউ সতী হতে রাজী হল না। মানসিক বিকারগ্রস্ত মেয়েটি আগুন দেখে শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসল। অগত্যা বড় বউ যে কিনা কোনওদিন স্বামীর ঘর করল না, তাকেই যেতে হল সহগমনে। কী বিচার! আবার এমন ঘটনাও দেখা যায় যে স্বামীর সঙ্গে একদিনও ঘর করেনি, সে স্বেচ্ছায় স্বামীর বুকের ওপর নিশ্চিন্তে মাথা দিয়ে ‘স্বর্গারোহন’ করেছে। মাঝে বৃষ্টি হয়ে চিতার আগুন নিভে সে আধপোড়া হয়ে শুয়ে আছে। তবুও তার বিকার নেই। ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে যখন আবার চিতায় আগুন জ্বালানো হল তার ভবলীলা সাঙ্গ হল।
বাংলায় যখন সতীদাহ প্রথার এমন রমরমা, তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সতীদাহর সংখ্যা নগণ্য, হাতে গোনা। চব্বিশ পরগণার আড়িয়াদহ, নৈহাটি, বৈদ্যবাটি, হরিপাল, সালকিয়া, চিৎপুর, কালনা-কাটোয়া, বিষ্ণুপুরে প্রায়ই সতীর চিতা জ্বলত। কেরীর তালিকা অনুযায়ী ১৮০৩ সালে সতী হয় ২৭৫ জন। ১৮০৪ সালে ছয় মাসে ১১৬ জন। অদ্ভুত ব্যাপার শিক্ষার হার যেখানে একটু বেশি সেখানেই সতীদাহর ঘটনা বেশি। ১৮২৩–এ ৫৭৫ জন সতী হয়। ১৮২৬–এ ৬৩৯ জনের মধ্যে কলকাতায় ৩৬৮ জন।
খ্রিস্টপূর্বকাল থেকেই ভারতে সতীদাহ’র মতো ঘটনা ঘটে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭–এ আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় পাঞ্জাবে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ‘রাজতরঙ্গিনী’তে আছে সতীর ঘটনা। বরাহমিহির সতীর গুণগান গেয়েছেন। মঙ্গলকাব্যে আছে সতীর উল্লেখ। মুলতান থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে ইবন বতুতা আমঝারিতে তিনজন মেয়েকে সতী হতে দেখে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আবার বার্নিয়েরের মতো কেউ কেউ সতী হওয়া থেকে কোনও কোনও মেয়েকে রক্ষা করেছেন। তাঁর নজর এড়ায়নি যে প্রধানত ব্রাহ্মণরা হিন্দু মেয়েদের সতী হতে উৎসাহ দিত। সবাই স্বেচ্ছায় সতী হত না। কিন্তু একটা বিধবা মেয়ের আজীবন ভরণপোষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অথবা তার সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য জোর করে তাকে চিতায় উঠতে বাধ্য করা হত।
স্বপন বসুর “বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস” বইতে পাই যে মেয়েরা সতী হলে কোনও কোনও ধনী পরিবার থেকে তখনকার সময় দুইশত টাকা অবধি সাম্মানিক জুটত। এই অর্থের লোভে ব্রাহ্মণরা মেয়েদের সতী হতে উৎসাহ দিত। স্বপন বসুর ‘সতী’ নামক বইতেই দেখি একটি অল্পবয়সি মেয়ের স্বামী মারা যেতে সে সতী হবে বলে মনস্থির করল। আত্মীয়স্বজন বেজায় খুশি। চারিদিকে সাজো সাজো রব। চিতার আগুন জ্বলে উঠতেই মেয়েটির কাকা মেয়েটিকে ধরে চিতায় তুলে দিল। আগুনে ঝলসে মেয়েটি বাঁচবার জন্য চিতা থেকে লাফ দিল। শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি। চিতা থেকে পালালে চলবে না। সংকল্প যখন করেছে তাকে সহমরণে যেতেই হবে। আধপোড়া মেয়েটা প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে একটা ঝোপের পিছনে আশ্রয় নিল। তার কাকা কিন্তু লোকজন সঙ্গে এনে তাকে ঠিক খুঁজে বের করে আবার জবরদস্তি করে চিতায় তুলে দিল। পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে পুরো পরিবারের মান সম্মান বাড়িয়ে দিয়ে গেল মেয়েটি।
আর একটি খুব অদ্ভুত গল্প পড়েছিলাম। একটি লোকের তিন বউ। প্রথমজনকে বিয়ে করে একদিনও সংসার করেননি। দ্বিতীয় স্ত্রী মানসিক বিকারগ্রস্ত। তাই তিনি তৃতীয় একজনকে বিয়ে করে তার সঙ্গে থাকতেন। তিনি মারা গেলে কে সতী হবে? ছোট বউ আর মানসিক বিকারগ্রস্ত বউটি বলল তারা সতী হবে। কিন্তু চিতার অমন ভয়াল রূপ দেখে ছোট বউ সতী হতে রাজী হল না। মানসিক বিকারগ্রস্ত মেয়েটি আগুন দেখে শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসল। অগত্যা বড় বউ যে কিনা কোনওদিন স্বামীর ঘর করল না, তাকেই যেতে হল সহগমনে। কী বিচার! আবার এমন ঘটনাও দেখা যায় যে স্বামীর সঙ্গে একদিনও ঘর করেনি, সে স্বেচ্ছায় স্বামীর বুকের ওপর নিশ্চিন্তে মাথা দিয়ে ‘স্বর্গারোহন’ করেছে। মাঝে বৃষ্টি হয়ে চিতার আগুন নিভে সে আধপোড়া হয়ে শুয়ে আছে। তবুও তার বিকার নেই। ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে যখন আবার চিতায় আগুন জ্বালানো হল তার ভবলীলা সাঙ্গ হল।
 বাংলায় সতী হওয়ার অনুষ্ঠানটিও ছিল অদ্ভুত। যে মেয়ে সতী হবে বলে মনস্থির করত সে স্নান করে নতুন কাপড় পরে পা আলতায় রাঙিয়ে একটি আমডাল নিয়ে শবের কাছে বসত। মাথার চুল বিছিয়ে দেওয়া হত। ছেলে বা নিকট আত্মীয় অনুষ্ঠানের সব জিনিস জড়ো করে চিতা প্রস্তুত করত। সে গায়ের গয়না খুলে সিঁদুরের টিপ পরে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে আঁচলে বাঁধা খই, কড়ি বা গয়না ছুড়ে ছুড়ে দিত উন্মত্ত জনতাকে। লোকে কাড়াকাড়ি করত ওগুলো পাওয়ার আশায়। তারপর বিচিত্র, গগনভেদী বাজনার মধ্যে দিয়ে সে চিতায় উঠত। মেয়েদের চিতার সঙ্গে বুকে, কোমরে, পায়ে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হত যাতে তারা পালিয়ে না যায়।
শুধু সহমরণ নয়, সমাজে তখন অনুমরণ, সহসমাধি, কতরকম প্রথা। স্বামীর সঙ্গে একসাথে পুড়ে মারা গেলে সহমরণ। স্বামীর মৃত্যুর সময় অনুপস্থিত থাকলে, অসুস্থ হলে বা গর্ভবতী হলে পরে স্বামীর ব্যবহৃত যে কোনও জিনিস যেমন লাঠি, চটি, থালা, বাঁধানো দাঁত, স্বামীর লেখা চিঠি ইত্যাদি নিয়ে চিতায় উঠত স্ত্রী। এটি হল ‘অনুমরণ’। যেমন ভোলা চামারের বউ উদাসীয়া। ভোলা মারা যাবার সাত বছর পরে সে ১৮২২ সালের ৫ মে ভোলার ব্যবহৃত থালা নিয়ে সতী হয়। কোঙ্কন অঞ্চলের মেয়েরা স্বামীর অনুরূপ এক চালের মূর্তি গড়ে অনুমৃতা হত। এটি ‘পলাশবুদি’।
বিজয়নগরের লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মেয়েরা (এরা গলায় শিবলিঙ্গ ঝুলিয়ে রাখে বলে এদের এমন নাম। এরা শৈব। দুই শ্রেণীযুক্ত। প্রথম স্মার্ত্ত বা শান্ত শৈব। দ্বিতীয়টি যোদ্ধৃ শৈব) স্বামীর সঙ্গে সহসমাধিস্হ হত। একটি গর্ত করে মেয়েটিকে নামিয়ে মাটি দিয়ে ভরাট করে তার উপর পাথর চাপিয়ে দেওয়া হত।
M. Martin সম্পাদিত The History Antiquities, Topography & Statistics of Eastern India (1838, Vol-1) বইটিতে পাওয়া যায় মুসলমান মেয়েরাও সতী হত। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে সতীদাহকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত ও সতীদাহে অংশগ্রহণ করত। কোনও কোনও মুসলমান মেয়ে স্বামীর সঙ্গে সহসমাধিস্হ হত। আবার পঞ্জাবে মা ছেলের সঙ্গে সতী হত। একে বলে ‘মা-সতী’। মৃত ভাই–এর চিতায় বোনের আত্মাহূতি দেবার ঘটনাও আছে। সেখানে বাবা নিজে একসঙ্গে পুত্র ও কন্যার চিতা সাজিয়ে অগ্নিসংযোগ করেছিল। ১৮১৮ সালের শেষদিকে চন্দননগরের এক তরুণী ভাবী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেয়। বিয়ের আগেরদিন ছেলেটি কলেরায় মারা যায়। মেয়েটি জোর করে সতী হয়। রক্ষিতারাও সতী হত। রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত সাধ্বী স্ত্রী সতী হবে না রক্ষিতা। সম্ভবত ১৮১৭ সালে সরকার আইন করে রক্ষিতাদের সহমৃতা হওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করে।
সতীদাহর রমরমা। মেয়েদের পড়াশোনার বালাই নেই। চার বছরের শিশু থেকে একশ বছরের বৃদ্ধা অবধি দেদার সতী হচ্ছে। লোকের চোখে দেবী হয়ে ওঠার লোভ যেমন আছে তেমনই স্বামী মারা গেলে মেয়েটি ব্যভিচারিণী হবে, উচ্ছৃঙ্খল হবে সেই সন্দেহে সমাজ তাদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা জানে না শাস্ত্রের বিধান, জানে না তারা পাপের ভাগীদার না পুণ্যের ভাগীদার। রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছে সতীদাহ হল শাস্ত্রীয় বিধি। মেয়েদের সপক্ষে কেউ নেই। উইলিয়াম কেরী একটু সচেষ্ট হন কিন্তু সাফল্য পাননি। পরে ১৮১৩ সালে সরকার পুলিশদের জবরদস্তি করে মাদক খাইয়ে সতী হওয়া রুখতে নির্দেশ দেন। ১৮১৫ সালে সতী হলে যেন পুলিশকে জানানো হয় এই মর্মে নির্দেশিকা দেওয়া হয়। কিন্তু সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বাংলায় এই প্রথা হু হু করে বাড়তে থাকে।
১৮১৭ সাল নাগাদ এগিয়ে এলেন যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। সর্বপ্রথম কলম ধরলেন সতীদাহর বিপক্ষে। লিখলেন — ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ’। সম্ভবত ১৮১৮ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হল। তিনি প্রবর্ত্তক (প্রবর্তক) ও নিবর্ত্তকের (নিবর্তক) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন সতীদাহ মোটেই আবশ্যিক নয়। এটা জ্ঞানত নারীহত্যা। তিনি মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করে দেখালেন যে স্বামী মারা গেলে মেয়েরা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মুক্তিলাভ করবে, সহমৃতা হয়ে নয়। তাছাড়া তিনি ওই ধরে বেঁধে সতীদাহর বিরুদ্ধে লিখলেন– “তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্পদেশ যে এই বাঙ্গলা ইহাতেই কিঞ্চিতকাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন বিশেষত কোনো ব্যক্তি যাহার লোকভয় ও ধর্ম্মভয় আছে সে এমত কহিবেক না যে পরম্পরাপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী বধ মনুষ্য বধ ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে…।” হিন্দুদের মনে বিধবা মেয়েদের ব্যভিচারের ভাবনাটিও তিনি ভ্রান্ত বলে দেখিয়ে দেন।
লেখাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আলোড়ন পড়ে যায়। গোঁড়া সম্প্রদায় প্রতিবাদে মুখর। কালাচাঁদ বসুর নির্দেশে কলকাতার ঘোষালবাগানের চতুষ্পাঠীর পরিচালক কাশীনাথ তর্কবাগীশ রামমোহনের লেখার প্রত্যুত্তরে লিখলেন “বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ”। সতীদাহর সমর্থনে তিনি লিখলেন–“দাহকেরা যে দেশাচারপ্রযুক্ত বন্ধনাদি করে সেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যে পূর্ব্বোক্ত হারীতবচনে বুঝাইয়াছে যাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী আত্মশরীরে প্রকৃষ্টরূপে দাহ না করে তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রীশরীর হইতে মুক্তা হয় না।” তিনি আরও বলেন ইতস্তত পড়ে থাকা দেহখণ্ডগুলি তুলে ভালো করে পোড়ালেও দোষ হয় না। রামমোহন এর উত্তরে ১৮১৯–এর নভেম্বরে লিখলেন “সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ”। কলকাতার মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হল। ১৯২০ সালে এটির ইংরেজি তর্জমা করে রামমোহন এটা মার্কুইস অব্ হেস্টিংসের স্ত্রী’র নামে উৎসর্গ করেন। ‘গবর্নমেন্ট গেজেট’ লিখল- ”রামমোহন রায় যুক্তির সাহায্যে তাঁর দেশবাসীকে দেখালেন সতীপ্রথা শাস্ত্রসম্মত নয়।” আলোড়ন তৈরি হল বাঙালি মনে।
বাংলায় সতী হওয়ার অনুষ্ঠানটিও ছিল অদ্ভুত। যে মেয়ে সতী হবে বলে মনস্থির করত সে স্নান করে নতুন কাপড় পরে পা আলতায় রাঙিয়ে একটি আমডাল নিয়ে শবের কাছে বসত। মাথার চুল বিছিয়ে দেওয়া হত। ছেলে বা নিকট আত্মীয় অনুষ্ঠানের সব জিনিস জড়ো করে চিতা প্রস্তুত করত। সে গায়ের গয়না খুলে সিঁদুরের টিপ পরে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে আঁচলে বাঁধা খই, কড়ি বা গয়না ছুড়ে ছুড়ে দিত উন্মত্ত জনতাকে। লোকে কাড়াকাড়ি করত ওগুলো পাওয়ার আশায়। তারপর বিচিত্র, গগনভেদী বাজনার মধ্যে দিয়ে সে চিতায় উঠত। মেয়েদের চিতার সঙ্গে বুকে, কোমরে, পায়ে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হত যাতে তারা পালিয়ে না যায়।
শুধু সহমরণ নয়, সমাজে তখন অনুমরণ, সহসমাধি, কতরকম প্রথা। স্বামীর সঙ্গে একসাথে পুড়ে মারা গেলে সহমরণ। স্বামীর মৃত্যুর সময় অনুপস্থিত থাকলে, অসুস্থ হলে বা গর্ভবতী হলে পরে স্বামীর ব্যবহৃত যে কোনও জিনিস যেমন লাঠি, চটি, থালা, বাঁধানো দাঁত, স্বামীর লেখা চিঠি ইত্যাদি নিয়ে চিতায় উঠত স্ত্রী। এটি হল ‘অনুমরণ’। যেমন ভোলা চামারের বউ উদাসীয়া। ভোলা মারা যাবার সাত বছর পরে সে ১৮২২ সালের ৫ মে ভোলার ব্যবহৃত থালা নিয়ে সতী হয়। কোঙ্কন অঞ্চলের মেয়েরা স্বামীর অনুরূপ এক চালের মূর্তি গড়ে অনুমৃতা হত। এটি ‘পলাশবুদি’।
বিজয়নগরের লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মেয়েরা (এরা গলায় শিবলিঙ্গ ঝুলিয়ে রাখে বলে এদের এমন নাম। এরা শৈব। দুই শ্রেণীযুক্ত। প্রথম স্মার্ত্ত বা শান্ত শৈব। দ্বিতীয়টি যোদ্ধৃ শৈব) স্বামীর সঙ্গে সহসমাধিস্হ হত। একটি গর্ত করে মেয়েটিকে নামিয়ে মাটি দিয়ে ভরাট করে তার উপর পাথর চাপিয়ে দেওয়া হত।
M. Martin সম্পাদিত The History Antiquities, Topography & Statistics of Eastern India (1838, Vol-1) বইটিতে পাওয়া যায় মুসলমান মেয়েরাও সতী হত। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে সতীদাহকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত ও সতীদাহে অংশগ্রহণ করত। কোনও কোনও মুসলমান মেয়ে স্বামীর সঙ্গে সহসমাধিস্হ হত। আবার পঞ্জাবে মা ছেলের সঙ্গে সতী হত। একে বলে ‘মা-সতী’। মৃত ভাই–এর চিতায় বোনের আত্মাহূতি দেবার ঘটনাও আছে। সেখানে বাবা নিজে একসঙ্গে পুত্র ও কন্যার চিতা সাজিয়ে অগ্নিসংযোগ করেছিল। ১৮১৮ সালের শেষদিকে চন্দননগরের এক তরুণী ভাবী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেয়। বিয়ের আগেরদিন ছেলেটি কলেরায় মারা যায়। মেয়েটি জোর করে সতী হয়। রক্ষিতারাও সতী হত। রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত সাধ্বী স্ত্রী সতী হবে না রক্ষিতা। সম্ভবত ১৮১৭ সালে সরকার আইন করে রক্ষিতাদের সহমৃতা হওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করে।
সতীদাহর রমরমা। মেয়েদের পড়াশোনার বালাই নেই। চার বছরের শিশু থেকে একশ বছরের বৃদ্ধা অবধি দেদার সতী হচ্ছে। লোকের চোখে দেবী হয়ে ওঠার লোভ যেমন আছে তেমনই স্বামী মারা গেলে মেয়েটি ব্যভিচারিণী হবে, উচ্ছৃঙ্খল হবে সেই সন্দেহে সমাজ তাদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা জানে না শাস্ত্রের বিধান, জানে না তারা পাপের ভাগীদার না পুণ্যের ভাগীদার। রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছে সতীদাহ হল শাস্ত্রীয় বিধি। মেয়েদের সপক্ষে কেউ নেই। উইলিয়াম কেরী একটু সচেষ্ট হন কিন্তু সাফল্য পাননি। পরে ১৮১৩ সালে সরকার পুলিশদের জবরদস্তি করে মাদক খাইয়ে সতী হওয়া রুখতে নির্দেশ দেন। ১৮১৫ সালে সতী হলে যেন পুলিশকে জানানো হয় এই মর্মে নির্দেশিকা দেওয়া হয়। কিন্তু সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বাংলায় এই প্রথা হু হু করে বাড়তে থাকে।
১৮১৭ সাল নাগাদ এগিয়ে এলেন যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। সর্বপ্রথম কলম ধরলেন সতীদাহর বিপক্ষে। লিখলেন — ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ’। সম্ভবত ১৮১৮ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হল। তিনি প্রবর্ত্তক (প্রবর্তক) ও নিবর্ত্তকের (নিবর্তক) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন সতীদাহ মোটেই আবশ্যিক নয়। এটা জ্ঞানত নারীহত্যা। তিনি মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করে দেখালেন যে স্বামী মারা গেলে মেয়েরা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মুক্তিলাভ করবে, সহমৃতা হয়ে নয়। তাছাড়া তিনি ওই ধরে বেঁধে সতীদাহর বিরুদ্ধে লিখলেন– “তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্পদেশ যে এই বাঙ্গলা ইহাতেই কিঞ্চিতকাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন বিশেষত কোনো ব্যক্তি যাহার লোকভয় ও ধর্ম্মভয় আছে সে এমত কহিবেক না যে পরম্পরাপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী বধ মনুষ্য বধ ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে…।” হিন্দুদের মনে বিধবা মেয়েদের ব্যভিচারের ভাবনাটিও তিনি ভ্রান্ত বলে দেখিয়ে দেন।
লেখাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আলোড়ন পড়ে যায়। গোঁড়া সম্প্রদায় প্রতিবাদে মুখর। কালাচাঁদ বসুর নির্দেশে কলকাতার ঘোষালবাগানের চতুষ্পাঠীর পরিচালক কাশীনাথ তর্কবাগীশ রামমোহনের লেখার প্রত্যুত্তরে লিখলেন “বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ”। সতীদাহর সমর্থনে তিনি লিখলেন–“দাহকেরা যে দেশাচারপ্রযুক্ত বন্ধনাদি করে সেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যে পূর্ব্বোক্ত হারীতবচনে বুঝাইয়াছে যাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী আত্মশরীরে প্রকৃষ্টরূপে দাহ না করে তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রীশরীর হইতে মুক্তা হয় না।” তিনি আরও বলেন ইতস্তত পড়ে থাকা দেহখণ্ডগুলি তুলে ভালো করে পোড়ালেও দোষ হয় না। রামমোহন এর উত্তরে ১৮১৯–এর নভেম্বরে লিখলেন “সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ”। কলকাতার মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হল। ১৯২০ সালে এটির ইংরেজি তর্জমা করে রামমোহন এটা মার্কুইস অব্ হেস্টিংসের স্ত্রী’র নামে উৎসর্গ করেন। ‘গবর্নমেন্ট গেজেট’ লিখল- ”রামমোহন রায় যুক্তির সাহায্যে তাঁর দেশবাসীকে দেখালেন সতীপ্রথা শাস্ত্রসম্মত নয়।” আলোড়ন তৈরি হল বাঙালি মনে।
 ইংরেজরা নড়েচড়ে বসল। তারা বুঝল হিন্দুদের মধ্যে এ প্রথা নিয়ে মতভেদ আছে। তারা এবার সাহস পেল। হেস্টিংস, আমর্হাস্ট মনে মনে চাইলেও দেশীয় প্রথায় হস্তক্ষেপ হলে পাছে গণ্ডগোল হয় সেই ভয়ে তাঁরা আইন করে সতীদাহ রদের পথ মাড়াননি। ১৮২৮ সালের জুলাই মাসে শাসনকর্তা হয়ে এলেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। তিনি নিরন্তর চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কলকাতার নিকটবর্তী ব্যাপটিস্ট ও মিশনারিরা তাঁকে অনুরোধ করল। বেন্টিঙ্ক রামমোহনকে অনুরোধ করলেন তাঁর মতামত জানাতে। রামমোহন তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করলেন।
সতীদাহপ্রথা রদ হতে পারে শুনে মাঠে নেমে পড়ল ‘সমাচার চন্দ্রিকা’। সম্পাদক ভবানীচরণ লিখলেন– “আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত শিউরে উঠছে। আমরা বিপন্ন, ভীত, বিস্মিত।” কিন্তু বেন্টিঙ্ক মেটকাফ, বেলি প্রমুখর সমর্থনে কাউন্সিলে ০৪/১২/১৮২৯ তারিখে সতীদাহকে “illegal and punishable act by criminal courts” বলে নিষিদ্ধ করলেন। খবরটা আসার সঙ্গে সঙ্গে সতীদাহ বিরোধীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। ইংরেজি সংবাদপত্র, বেঙ্গল হরকরা এটিকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাল। রামমোহনের নেতৃত্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরিহর দত্ত, কালীনাথ রায় প্রমুখ ১৮৩০ সালের ১৬ জানুয়ারি বেন্টিঙ্কের সঙ্গে দেখা করে তিনশ প্রজার সইসহ অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন। ইংরেজিতে পাঠ করেন হরিহর দত্ত। তাঁরা সস্ত্রীক বেন্টিঙ্ককে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
১৮৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি সতীদাহ রদ নিবারণে পথে নামল রাজা রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন ঠাকুর, গোকুলনাথ মল্লিকের নেতৃত্বে ‘ধর্মসভা’। এই সভাকে ব্যঙ্গ করে বলা হত ‘গুড়ুম সভা’। গুড়ুম সভার সদস্যরা সতীর ঘোর সমর্থক। তাঁরা সংস্কৃত কলেজের সামনে রাজপথে নামলেন। ঠিক হল ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে এই আইনের বিরুদ্ধে তাঁরা আপিল করবেন। ছয় মাসে উনিশটি সভা করে তাঁরা প্রায় এগারোশ জনের সইসহ একটি আবেদনপত্র তৈরি করেন। কিন্তু কালাপানি পেরিয়ে নিয়ে যাবে কে? পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি ফ্রান্সিস বেথিকে ধরলেন। বেথির এ ভূমিকার জন্য তিনি ইংলণ্ডে নিন্দিত হলেন।
রামমোহন প্রানপণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেন সতীদাহ যাতে আর ফিরে না আসে। পাল্টা আবেদন করার জন্য ও কোম্পানির সনদ আইনের জন্য তিনি ইংল্যান্ড যাওয়া মনস্থির করলেন। তাঁর ইংল্যান্ড যাওয়ার ইচ্ছে বহুদিনের। সেই সময় দিল্লির বাদশাও নিজের কিছু দরকারে রামমোহনকে ইংল্যান্ড পাঠাবেন ভাবছিলেন। তিনি রামমোহনকে ১৮২৯ সালের আগস্ট মাসে ‘রাজা’ উপাধিতে ভূষিত করলেন এবং তাঁর দূত হিসেবে নিয়োগ করলেন। ১৮৩০ সালের ১৫ নভেম্বর রামমোহন ‘এলবিয়ন’ জাহাজে ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন। ১৮৩১–এর ৮ এপ্রিল পৌঁছালেন লিভারপুল। সেখান থেকে লণ্ডন। জেরেমি বেন্থাম এলেন দেখা করতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁর সম্মানে যে ভোজসভা দিল সেখানে শুধু তিনি ভাত আর জল ছাড়া কিছুই খাননি। এরমধ্যে তিনি লর্ড ল্যান্সডাউনের সঙ্গে দেখা করে ভারতের সতী বিরোধীদের আবেদন আর নিজের মতামত ব্যক্ত করে এলেন। সেই আবেদনটি ল্যান্সডাউন ১৮৩১ সালের ১ জুলাই হাউস অফ লর্ডসে পেশ করেন।
১৮৩২–এর জুলাই মাসে প্রিভি কাউন্সিলে শুনানি শুরু হল। রামমোহন সেখানে উপস্থিত হয়ে আলোচনা শুনতেন। ১২ জুলাই সতী সমর্থকদের আবেদন বাতিল হয়ে গেল। চিরকালের জন্য ভারতবর্ষে বন্ধ হয়ে গেল সতীদাহ’র মতো অমানবিক, নিষ্ঠুর প্রথা। রামমোহন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নভেম্বরের শুরুর দিকে খবর এল দেশে। আনন্দে ফেটে পড়ল সতী বিরোধী পক্ষ বা ‘শীতল সভা’। তাঁরা ১৮৩২–এর ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ছ’টায় জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজে জয়োল্লাস সভার আয়োজন করলেন। কে নেই সে সভায়! ডেভিড হেয়ার, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলোচন ঘোষ, রামমোহন পুত্র রাধাপ্রসাদ প্রমুখ।
সেই সভায় চন্দ্রশেখর দেব যখন রামমোহনকে এই কৃতিত্ব দেওয়ার কথা বলেন তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন–“Babu Krishna Mohana Banerjea is seconding the above spoke of the Raja’s perseverance against the Suttee. He referred to Raja’s moral strength in standing the first Hindoo against some of the glaring superstitions of the country, and above all, against the inhuman rite of Suttee.”
রামমোহন রায় সমাজের সমস্ত অপমান, উপহাস উপেক্ষা করে দৃঢ়চেতা হয়ে নিজ লক্ষ্যে অটল থেকেছেন। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি সতীদাহ আন্দোলনকে সংগঠিত করেছেন, এক নির্দিষ্ট পথে চালনা করেছেন এবং মানুষের মনের ভ্রান্তি দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। মেয়েদের নবজীবন দান করেছেন তিনি। তাঁর অবদান আজীবন বাঙালি তথা ভারতবাসী কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে। তিনি যথার্থই ভারত পথিক।
তথ্যঋণ
১. রামমোহন রচনাবলী(১৯৭৩)
২. সতী– স্বপন বসু
৩. বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস(২০১৬)– স্বপন বসু
৪. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা(২০০৯)– বিনয় ঘোষ
৫. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ(২০১১)– বিনয় ঘোষ
৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯কল্প দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৩৮
৭. Parliamentary Papers(HOC),1825,Vol-XXIV
৮. Parliamentary Papers(HOC), 1825, Vol-XVIII.
ইংরেজরা নড়েচড়ে বসল। তারা বুঝল হিন্দুদের মধ্যে এ প্রথা নিয়ে মতভেদ আছে। তারা এবার সাহস পেল। হেস্টিংস, আমর্হাস্ট মনে মনে চাইলেও দেশীয় প্রথায় হস্তক্ষেপ হলে পাছে গণ্ডগোল হয় সেই ভয়ে তাঁরা আইন করে সতীদাহ রদের পথ মাড়াননি। ১৮২৮ সালের জুলাই মাসে শাসনকর্তা হয়ে এলেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। তিনি নিরন্তর চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কলকাতার নিকটবর্তী ব্যাপটিস্ট ও মিশনারিরা তাঁকে অনুরোধ করল। বেন্টিঙ্ক রামমোহনকে অনুরোধ করলেন তাঁর মতামত জানাতে। রামমোহন তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করলেন।
সতীদাহপ্রথা রদ হতে পারে শুনে মাঠে নেমে পড়ল ‘সমাচার চন্দ্রিকা’। সম্পাদক ভবানীচরণ লিখলেন– “আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত শিউরে উঠছে। আমরা বিপন্ন, ভীত, বিস্মিত।” কিন্তু বেন্টিঙ্ক মেটকাফ, বেলি প্রমুখর সমর্থনে কাউন্সিলে ০৪/১২/১৮২৯ তারিখে সতীদাহকে “illegal and punishable act by criminal courts” বলে নিষিদ্ধ করলেন। খবরটা আসার সঙ্গে সঙ্গে সতীদাহ বিরোধীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। ইংরেজি সংবাদপত্র, বেঙ্গল হরকরা এটিকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাল। রামমোহনের নেতৃত্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরিহর দত্ত, কালীনাথ রায় প্রমুখ ১৮৩০ সালের ১৬ জানুয়ারি বেন্টিঙ্কের সঙ্গে দেখা করে তিনশ প্রজার সইসহ অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন। ইংরেজিতে পাঠ করেন হরিহর দত্ত। তাঁরা সস্ত্রীক বেন্টিঙ্ককে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
১৮৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি সতীদাহ রদ নিবারণে পথে নামল রাজা রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন ঠাকুর, গোকুলনাথ মল্লিকের নেতৃত্বে ‘ধর্মসভা’। এই সভাকে ব্যঙ্গ করে বলা হত ‘গুড়ুম সভা’। গুড়ুম সভার সদস্যরা সতীর ঘোর সমর্থক। তাঁরা সংস্কৃত কলেজের সামনে রাজপথে নামলেন। ঠিক হল ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে এই আইনের বিরুদ্ধে তাঁরা আপিল করবেন। ছয় মাসে উনিশটি সভা করে তাঁরা প্রায় এগারোশ জনের সইসহ একটি আবেদনপত্র তৈরি করেন। কিন্তু কালাপানি পেরিয়ে নিয়ে যাবে কে? পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি ফ্রান্সিস বেথিকে ধরলেন। বেথির এ ভূমিকার জন্য তিনি ইংলণ্ডে নিন্দিত হলেন।
রামমোহন প্রানপণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেন সতীদাহ যাতে আর ফিরে না আসে। পাল্টা আবেদন করার জন্য ও কোম্পানির সনদ আইনের জন্য তিনি ইংল্যান্ড যাওয়া মনস্থির করলেন। তাঁর ইংল্যান্ড যাওয়ার ইচ্ছে বহুদিনের। সেই সময় দিল্লির বাদশাও নিজের কিছু দরকারে রামমোহনকে ইংল্যান্ড পাঠাবেন ভাবছিলেন। তিনি রামমোহনকে ১৮২৯ সালের আগস্ট মাসে ‘রাজা’ উপাধিতে ভূষিত করলেন এবং তাঁর দূত হিসেবে নিয়োগ করলেন। ১৮৩০ সালের ১৫ নভেম্বর রামমোহন ‘এলবিয়ন’ জাহাজে ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন। ১৮৩১–এর ৮ এপ্রিল পৌঁছালেন লিভারপুল। সেখান থেকে লণ্ডন। জেরেমি বেন্থাম এলেন দেখা করতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁর সম্মানে যে ভোজসভা দিল সেখানে শুধু তিনি ভাত আর জল ছাড়া কিছুই খাননি। এরমধ্যে তিনি লর্ড ল্যান্সডাউনের সঙ্গে দেখা করে ভারতের সতী বিরোধীদের আবেদন আর নিজের মতামত ব্যক্ত করে এলেন। সেই আবেদনটি ল্যান্সডাউন ১৮৩১ সালের ১ জুলাই হাউস অফ লর্ডসে পেশ করেন।
১৮৩২–এর জুলাই মাসে প্রিভি কাউন্সিলে শুনানি শুরু হল। রামমোহন সেখানে উপস্থিত হয়ে আলোচনা শুনতেন। ১২ জুলাই সতী সমর্থকদের আবেদন বাতিল হয়ে গেল। চিরকালের জন্য ভারতবর্ষে বন্ধ হয়ে গেল সতীদাহ’র মতো অমানবিক, নিষ্ঠুর প্রথা। রামমোহন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নভেম্বরের শুরুর দিকে খবর এল দেশে। আনন্দে ফেটে পড়ল সতী বিরোধী পক্ষ বা ‘শীতল সভা’। তাঁরা ১৮৩২–এর ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ছ’টায় জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজে জয়োল্লাস সভার আয়োজন করলেন। কে নেই সে সভায়! ডেভিড হেয়ার, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলোচন ঘোষ, রামমোহন পুত্র রাধাপ্রসাদ প্রমুখ।
সেই সভায় চন্দ্রশেখর দেব যখন রামমোহনকে এই কৃতিত্ব দেওয়ার কথা বলেন তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন–“Babu Krishna Mohana Banerjea is seconding the above spoke of the Raja’s perseverance against the Suttee. He referred to Raja’s moral strength in standing the first Hindoo against some of the glaring superstitions of the country, and above all, against the inhuman rite of Suttee.”
রামমোহন রায় সমাজের সমস্ত অপমান, উপহাস উপেক্ষা করে দৃঢ়চেতা হয়ে নিজ লক্ষ্যে অটল থেকেছেন। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি সতীদাহ আন্দোলনকে সংগঠিত করেছেন, এক নির্দিষ্ট পথে চালনা করেছেন এবং মানুষের মনের ভ্রান্তি দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। মেয়েদের নবজীবন দান করেছেন তিনি। তাঁর অবদান আজীবন বাঙালি তথা ভারতবাসী কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে। তিনি যথার্থই ভারত পথিক।
তথ্যঋণ
১. রামমোহন রচনাবলী(১৯৭৩)
২. সতী– স্বপন বসু
৩. বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস(২০১৬)– স্বপন বসু
৪. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা(২০০৯)– বিনয় ঘোষ
৫. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ(২০১১)– বিনয় ঘোষ
৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯কল্প দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৩৮
৭. Parliamentary Papers(HOC),1825,Vol-XXIV
৮. Parliamentary Papers(HOC), 1825, Vol-XVIII.
 বাংলায় যখন সতীদাহ প্রথার এমন রমরমা, তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সতীদাহর সংখ্যা নগণ্য, হাতে গোনা। চব্বিশ পরগণার আড়িয়াদহ, নৈহাটি, বৈদ্যবাটি, হরিপাল, সালকিয়া, চিৎপুর, কালনা-কাটোয়া, বিষ্ণুপুরে প্রায়ই সতীর চিতা জ্বলত। কেরীর তালিকা অনুযায়ী ১৮০৩ সালে সতী হয় ২৭৫ জন। ১৮০৪ সালে ছয় মাসে ১১৬ জন। অদ্ভুত ব্যাপার শিক্ষার হার যেখানে একটু বেশি সেখানেই সতীদাহর ঘটনা বেশি। ১৮২৩–এ ৫৭৫ জন সতী হয়। ১৮২৬–এ ৬৩৯ জনের মধ্যে কলকাতায় ৩৬৮ জন।
খ্রিস্টপূর্বকাল থেকেই ভারতে সতীদাহ’র মতো ঘটনা ঘটে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭–এ আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় পাঞ্জাবে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ‘রাজতরঙ্গিনী’তে আছে সতীর ঘটনা। বরাহমিহির সতীর গুণগান গেয়েছেন। মঙ্গলকাব্যে আছে সতীর উল্লেখ। মুলতান থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে ইবন বতুতা আমঝারিতে তিনজন মেয়েকে সতী হতে দেখে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আবার বার্নিয়েরের মতো কেউ কেউ সতী হওয়া থেকে কোনও কোনও মেয়েকে রক্ষা করেছেন। তাঁর নজর এড়ায়নি যে প্রধানত ব্রাহ্মণরা হিন্দু মেয়েদের সতী হতে উৎসাহ দিত। সবাই স্বেচ্ছায় সতী হত না। কিন্তু একটা বিধবা মেয়ের আজীবন ভরণপোষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অথবা তার সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য জোর করে তাকে চিতায় উঠতে বাধ্য করা হত।
স্বপন বসুর “বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস” বইতে পাই যে মেয়েরা সতী হলে কোনও কোনও ধনী পরিবার থেকে তখনকার সময় দুইশত টাকা অবধি সাম্মানিক জুটত। এই অর্থের লোভে ব্রাহ্মণরা মেয়েদের সতী হতে উৎসাহ দিত। স্বপন বসুর ‘সতী’ নামক বইতেই দেখি একটি অল্পবয়সি মেয়ের স্বামী মারা যেতে সে সতী হবে বলে মনস্থির করল। আত্মীয়স্বজন বেজায় খুশি। চারিদিকে সাজো সাজো রব। চিতার আগুন জ্বলে উঠতেই মেয়েটির কাকা মেয়েটিকে ধরে চিতায় তুলে দিল। আগুনে ঝলসে মেয়েটি বাঁচবার জন্য চিতা থেকে লাফ দিল। শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি। চিতা থেকে পালালে চলবে না। সংকল্প যখন করেছে তাকে সহমরণে যেতেই হবে। আধপোড়া মেয়েটা প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে একটা ঝোপের পিছনে আশ্রয় নিল। তার কাকা কিন্তু লোকজন সঙ্গে এনে তাকে ঠিক খুঁজে বের করে আবার জবরদস্তি করে চিতায় তুলে দিল। পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে পুরো পরিবারের মান সম্মান বাড়িয়ে দিয়ে গেল মেয়েটি।
আর একটি খুব অদ্ভুত গল্প পড়েছিলাম। একটি লোকের তিন বউ। প্রথমজনকে বিয়ে করে একদিনও সংসার করেননি। দ্বিতীয় স্ত্রী মানসিক বিকারগ্রস্ত। তাই তিনি তৃতীয় একজনকে বিয়ে করে তার সঙ্গে থাকতেন। তিনি মারা গেলে কে সতী হবে? ছোট বউ আর মানসিক বিকারগ্রস্ত বউটি বলল তারা সতী হবে। কিন্তু চিতার অমন ভয়াল রূপ দেখে ছোট বউ সতী হতে রাজী হল না। মানসিক বিকারগ্রস্ত মেয়েটি আগুন দেখে শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসল। অগত্যা বড় বউ যে কিনা কোনওদিন স্বামীর ঘর করল না, তাকেই যেতে হল সহগমনে। কী বিচার! আবার এমন ঘটনাও দেখা যায় যে স্বামীর সঙ্গে একদিনও ঘর করেনি, সে স্বেচ্ছায় স্বামীর বুকের ওপর নিশ্চিন্তে মাথা দিয়ে ‘স্বর্গারোহন’ করেছে। মাঝে বৃষ্টি হয়ে চিতার আগুন নিভে সে আধপোড়া হয়ে শুয়ে আছে। তবুও তার বিকার নেই। ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে যখন আবার চিতায় আগুন জ্বালানো হল তার ভবলীলা সাঙ্গ হল।
বাংলায় যখন সতীদাহ প্রথার এমন রমরমা, তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সতীদাহর সংখ্যা নগণ্য, হাতে গোনা। চব্বিশ পরগণার আড়িয়াদহ, নৈহাটি, বৈদ্যবাটি, হরিপাল, সালকিয়া, চিৎপুর, কালনা-কাটোয়া, বিষ্ণুপুরে প্রায়ই সতীর চিতা জ্বলত। কেরীর তালিকা অনুযায়ী ১৮০৩ সালে সতী হয় ২৭৫ জন। ১৮০৪ সালে ছয় মাসে ১১৬ জন। অদ্ভুত ব্যাপার শিক্ষার হার যেখানে একটু বেশি সেখানেই সতীদাহর ঘটনা বেশি। ১৮২৩–এ ৫৭৫ জন সতী হয়। ১৮২৬–এ ৬৩৯ জনের মধ্যে কলকাতায় ৩৬৮ জন।
খ্রিস্টপূর্বকাল থেকেই ভারতে সতীদাহ’র মতো ঘটনা ঘটে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭–এ আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় পাঞ্জাবে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ‘রাজতরঙ্গিনী’তে আছে সতীর ঘটনা। বরাহমিহির সতীর গুণগান গেয়েছেন। মঙ্গলকাব্যে আছে সতীর উল্লেখ। মুলতান থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে ইবন বতুতা আমঝারিতে তিনজন মেয়েকে সতী হতে দেখে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আবার বার্নিয়েরের মতো কেউ কেউ সতী হওয়া থেকে কোনও কোনও মেয়েকে রক্ষা করেছেন। তাঁর নজর এড়ায়নি যে প্রধানত ব্রাহ্মণরা হিন্দু মেয়েদের সতী হতে উৎসাহ দিত। সবাই স্বেচ্ছায় সতী হত না। কিন্তু একটা বিধবা মেয়ের আজীবন ভরণপোষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অথবা তার সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য জোর করে তাকে চিতায় উঠতে বাধ্য করা হত।
স্বপন বসুর “বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস” বইতে পাই যে মেয়েরা সতী হলে কোনও কোনও ধনী পরিবার থেকে তখনকার সময় দুইশত টাকা অবধি সাম্মানিক জুটত। এই অর্থের লোভে ব্রাহ্মণরা মেয়েদের সতী হতে উৎসাহ দিত। স্বপন বসুর ‘সতী’ নামক বইতেই দেখি একটি অল্পবয়সি মেয়ের স্বামী মারা যেতে সে সতী হবে বলে মনস্থির করল। আত্মীয়স্বজন বেজায় খুশি। চারিদিকে সাজো সাজো রব। চিতার আগুন জ্বলে উঠতেই মেয়েটির কাকা মেয়েটিকে ধরে চিতায় তুলে দিল। আগুনে ঝলসে মেয়েটি বাঁচবার জন্য চিতা থেকে লাফ দিল। শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি। চিতা থেকে পালালে চলবে না। সংকল্প যখন করেছে তাকে সহমরণে যেতেই হবে। আধপোড়া মেয়েটা প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে একটা ঝোপের পিছনে আশ্রয় নিল। তার কাকা কিন্তু লোকজন সঙ্গে এনে তাকে ঠিক খুঁজে বের করে আবার জবরদস্তি করে চিতায় তুলে দিল। পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে পুরো পরিবারের মান সম্মান বাড়িয়ে দিয়ে গেল মেয়েটি।
আর একটি খুব অদ্ভুত গল্প পড়েছিলাম। একটি লোকের তিন বউ। প্রথমজনকে বিয়ে করে একদিনও সংসার করেননি। দ্বিতীয় স্ত্রী মানসিক বিকারগ্রস্ত। তাই তিনি তৃতীয় একজনকে বিয়ে করে তার সঙ্গে থাকতেন। তিনি মারা গেলে কে সতী হবে? ছোট বউ আর মানসিক বিকারগ্রস্ত বউটি বলল তারা সতী হবে। কিন্তু চিতার অমন ভয়াল রূপ দেখে ছোট বউ সতী হতে রাজী হল না। মানসিক বিকারগ্রস্ত মেয়েটি আগুন দেখে শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসল। অগত্যা বড় বউ যে কিনা কোনওদিন স্বামীর ঘর করল না, তাকেই যেতে হল সহগমনে। কী বিচার! আবার এমন ঘটনাও দেখা যায় যে স্বামীর সঙ্গে একদিনও ঘর করেনি, সে স্বেচ্ছায় স্বামীর বুকের ওপর নিশ্চিন্তে মাথা দিয়ে ‘স্বর্গারোহন’ করেছে। মাঝে বৃষ্টি হয়ে চিতার আগুন নিভে সে আধপোড়া হয়ে শুয়ে আছে। তবুও তার বিকার নেই। ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে যখন আবার চিতায় আগুন জ্বালানো হল তার ভবলীলা সাঙ্গ হল।
 বাংলায় সতী হওয়ার অনুষ্ঠানটিও ছিল অদ্ভুত। যে মেয়ে সতী হবে বলে মনস্থির করত সে স্নান করে নতুন কাপড় পরে পা আলতায় রাঙিয়ে একটি আমডাল নিয়ে শবের কাছে বসত। মাথার চুল বিছিয়ে দেওয়া হত। ছেলে বা নিকট আত্মীয় অনুষ্ঠানের সব জিনিস জড়ো করে চিতা প্রস্তুত করত। সে গায়ের গয়না খুলে সিঁদুরের টিপ পরে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে আঁচলে বাঁধা খই, কড়ি বা গয়না ছুড়ে ছুড়ে দিত উন্মত্ত জনতাকে। লোকে কাড়াকাড়ি করত ওগুলো পাওয়ার আশায়। তারপর বিচিত্র, গগনভেদী বাজনার মধ্যে দিয়ে সে চিতায় উঠত। মেয়েদের চিতার সঙ্গে বুকে, কোমরে, পায়ে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হত যাতে তারা পালিয়ে না যায়।
শুধু সহমরণ নয়, সমাজে তখন অনুমরণ, সহসমাধি, কতরকম প্রথা। স্বামীর সঙ্গে একসাথে পুড়ে মারা গেলে সহমরণ। স্বামীর মৃত্যুর সময় অনুপস্থিত থাকলে, অসুস্থ হলে বা গর্ভবতী হলে পরে স্বামীর ব্যবহৃত যে কোনও জিনিস যেমন লাঠি, চটি, থালা, বাঁধানো দাঁত, স্বামীর লেখা চিঠি ইত্যাদি নিয়ে চিতায় উঠত স্ত্রী। এটি হল ‘অনুমরণ’। যেমন ভোলা চামারের বউ উদাসীয়া। ভোলা মারা যাবার সাত বছর পরে সে ১৮২২ সালের ৫ মে ভোলার ব্যবহৃত থালা নিয়ে সতী হয়। কোঙ্কন অঞ্চলের মেয়েরা স্বামীর অনুরূপ এক চালের মূর্তি গড়ে অনুমৃতা হত। এটি ‘পলাশবুদি’।
বিজয়নগরের লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মেয়েরা (এরা গলায় শিবলিঙ্গ ঝুলিয়ে রাখে বলে এদের এমন নাম। এরা শৈব। দুই শ্রেণীযুক্ত। প্রথম স্মার্ত্ত বা শান্ত শৈব। দ্বিতীয়টি যোদ্ধৃ শৈব) স্বামীর সঙ্গে সহসমাধিস্হ হত। একটি গর্ত করে মেয়েটিকে নামিয়ে মাটি দিয়ে ভরাট করে তার উপর পাথর চাপিয়ে দেওয়া হত।
M. Martin সম্পাদিত The History Antiquities, Topography & Statistics of Eastern India (1838, Vol-1) বইটিতে পাওয়া যায় মুসলমান মেয়েরাও সতী হত। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে সতীদাহকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত ও সতীদাহে অংশগ্রহণ করত। কোনও কোনও মুসলমান মেয়ে স্বামীর সঙ্গে সহসমাধিস্হ হত। আবার পঞ্জাবে মা ছেলের সঙ্গে সতী হত। একে বলে ‘মা-সতী’। মৃত ভাই–এর চিতায় বোনের আত্মাহূতি দেবার ঘটনাও আছে। সেখানে বাবা নিজে একসঙ্গে পুত্র ও কন্যার চিতা সাজিয়ে অগ্নিসংযোগ করেছিল। ১৮১৮ সালের শেষদিকে চন্দননগরের এক তরুণী ভাবী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেয়। বিয়ের আগেরদিন ছেলেটি কলেরায় মারা যায়। মেয়েটি জোর করে সতী হয়। রক্ষিতারাও সতী হত। রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত সাধ্বী স্ত্রী সতী হবে না রক্ষিতা। সম্ভবত ১৮১৭ সালে সরকার আইন করে রক্ষিতাদের সহমৃতা হওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করে।
সতীদাহর রমরমা। মেয়েদের পড়াশোনার বালাই নেই। চার বছরের শিশু থেকে একশ বছরের বৃদ্ধা অবধি দেদার সতী হচ্ছে। লোকের চোখে দেবী হয়ে ওঠার লোভ যেমন আছে তেমনই স্বামী মারা গেলে মেয়েটি ব্যভিচারিণী হবে, উচ্ছৃঙ্খল হবে সেই সন্দেহে সমাজ তাদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা জানে না শাস্ত্রের বিধান, জানে না তারা পাপের ভাগীদার না পুণ্যের ভাগীদার। রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছে সতীদাহ হল শাস্ত্রীয় বিধি। মেয়েদের সপক্ষে কেউ নেই। উইলিয়াম কেরী একটু সচেষ্ট হন কিন্তু সাফল্য পাননি। পরে ১৮১৩ সালে সরকার পুলিশদের জবরদস্তি করে মাদক খাইয়ে সতী হওয়া রুখতে নির্দেশ দেন। ১৮১৫ সালে সতী হলে যেন পুলিশকে জানানো হয় এই মর্মে নির্দেশিকা দেওয়া হয়। কিন্তু সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বাংলায় এই প্রথা হু হু করে বাড়তে থাকে।
১৮১৭ সাল নাগাদ এগিয়ে এলেন যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। সর্বপ্রথম কলম ধরলেন সতীদাহর বিপক্ষে। লিখলেন — ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ’। সম্ভবত ১৮১৮ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হল। তিনি প্রবর্ত্তক (প্রবর্তক) ও নিবর্ত্তকের (নিবর্তক) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন সতীদাহ মোটেই আবশ্যিক নয়। এটা জ্ঞানত নারীহত্যা। তিনি মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করে দেখালেন যে স্বামী মারা গেলে মেয়েরা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মুক্তিলাভ করবে, সহমৃতা হয়ে নয়। তাছাড়া তিনি ওই ধরে বেঁধে সতীদাহর বিরুদ্ধে লিখলেন– “তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্পদেশ যে এই বাঙ্গলা ইহাতেই কিঞ্চিতকাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন বিশেষত কোনো ব্যক্তি যাহার লোকভয় ও ধর্ম্মভয় আছে সে এমত কহিবেক না যে পরম্পরাপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী বধ মনুষ্য বধ ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে…।” হিন্দুদের মনে বিধবা মেয়েদের ব্যভিচারের ভাবনাটিও তিনি ভ্রান্ত বলে দেখিয়ে দেন।
লেখাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আলোড়ন পড়ে যায়। গোঁড়া সম্প্রদায় প্রতিবাদে মুখর। কালাচাঁদ বসুর নির্দেশে কলকাতার ঘোষালবাগানের চতুষ্পাঠীর পরিচালক কাশীনাথ তর্কবাগীশ রামমোহনের লেখার প্রত্যুত্তরে লিখলেন “বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ”। সতীদাহর সমর্থনে তিনি লিখলেন–“দাহকেরা যে দেশাচারপ্রযুক্ত বন্ধনাদি করে সেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যে পূর্ব্বোক্ত হারীতবচনে বুঝাইয়াছে যাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী আত্মশরীরে প্রকৃষ্টরূপে দাহ না করে তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রীশরীর হইতে মুক্তা হয় না।” তিনি আরও বলেন ইতস্তত পড়ে থাকা দেহখণ্ডগুলি তুলে ভালো করে পোড়ালেও দোষ হয় না। রামমোহন এর উত্তরে ১৮১৯–এর নভেম্বরে লিখলেন “সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ”। কলকাতার মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হল। ১৯২০ সালে এটির ইংরেজি তর্জমা করে রামমোহন এটা মার্কুইস অব্ হেস্টিংসের স্ত্রী’র নামে উৎসর্গ করেন। ‘গবর্নমেন্ট গেজেট’ লিখল- ”রামমোহন রায় যুক্তির সাহায্যে তাঁর দেশবাসীকে দেখালেন সতীপ্রথা শাস্ত্রসম্মত নয়।” আলোড়ন তৈরি হল বাঙালি মনে।
বাংলায় সতী হওয়ার অনুষ্ঠানটিও ছিল অদ্ভুত। যে মেয়ে সতী হবে বলে মনস্থির করত সে স্নান করে নতুন কাপড় পরে পা আলতায় রাঙিয়ে একটি আমডাল নিয়ে শবের কাছে বসত। মাথার চুল বিছিয়ে দেওয়া হত। ছেলে বা নিকট আত্মীয় অনুষ্ঠানের সব জিনিস জড়ো করে চিতা প্রস্তুত করত। সে গায়ের গয়না খুলে সিঁদুরের টিপ পরে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে আঁচলে বাঁধা খই, কড়ি বা গয়না ছুড়ে ছুড়ে দিত উন্মত্ত জনতাকে। লোকে কাড়াকাড়ি করত ওগুলো পাওয়ার আশায়। তারপর বিচিত্র, গগনভেদী বাজনার মধ্যে দিয়ে সে চিতায় উঠত। মেয়েদের চিতার সঙ্গে বুকে, কোমরে, পায়ে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হত যাতে তারা পালিয়ে না যায়।
শুধু সহমরণ নয়, সমাজে তখন অনুমরণ, সহসমাধি, কতরকম প্রথা। স্বামীর সঙ্গে একসাথে পুড়ে মারা গেলে সহমরণ। স্বামীর মৃত্যুর সময় অনুপস্থিত থাকলে, অসুস্থ হলে বা গর্ভবতী হলে পরে স্বামীর ব্যবহৃত যে কোনও জিনিস যেমন লাঠি, চটি, থালা, বাঁধানো দাঁত, স্বামীর লেখা চিঠি ইত্যাদি নিয়ে চিতায় উঠত স্ত্রী। এটি হল ‘অনুমরণ’। যেমন ভোলা চামারের বউ উদাসীয়া। ভোলা মারা যাবার সাত বছর পরে সে ১৮২২ সালের ৫ মে ভোলার ব্যবহৃত থালা নিয়ে সতী হয়। কোঙ্কন অঞ্চলের মেয়েরা স্বামীর অনুরূপ এক চালের মূর্তি গড়ে অনুমৃতা হত। এটি ‘পলাশবুদি’।
বিজয়নগরের লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মেয়েরা (এরা গলায় শিবলিঙ্গ ঝুলিয়ে রাখে বলে এদের এমন নাম। এরা শৈব। দুই শ্রেণীযুক্ত। প্রথম স্মার্ত্ত বা শান্ত শৈব। দ্বিতীয়টি যোদ্ধৃ শৈব) স্বামীর সঙ্গে সহসমাধিস্হ হত। একটি গর্ত করে মেয়েটিকে নামিয়ে মাটি দিয়ে ভরাট করে তার উপর পাথর চাপিয়ে দেওয়া হত।
M. Martin সম্পাদিত The History Antiquities, Topography & Statistics of Eastern India (1838, Vol-1) বইটিতে পাওয়া যায় মুসলমান মেয়েরাও সতী হত। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে সতীদাহকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত ও সতীদাহে অংশগ্রহণ করত। কোনও কোনও মুসলমান মেয়ে স্বামীর সঙ্গে সহসমাধিস্হ হত। আবার পঞ্জাবে মা ছেলের সঙ্গে সতী হত। একে বলে ‘মা-সতী’। মৃত ভাই–এর চিতায় বোনের আত্মাহূতি দেবার ঘটনাও আছে। সেখানে বাবা নিজে একসঙ্গে পুত্র ও কন্যার চিতা সাজিয়ে অগ্নিসংযোগ করেছিল। ১৮১৮ সালের শেষদিকে চন্দননগরের এক তরুণী ভাবী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেয়। বিয়ের আগেরদিন ছেলেটি কলেরায় মারা যায়। মেয়েটি জোর করে সতী হয়। রক্ষিতারাও সতী হত। রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত সাধ্বী স্ত্রী সতী হবে না রক্ষিতা। সম্ভবত ১৮১৭ সালে সরকার আইন করে রক্ষিতাদের সহমৃতা হওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করে।
সতীদাহর রমরমা। মেয়েদের পড়াশোনার বালাই নেই। চার বছরের শিশু থেকে একশ বছরের বৃদ্ধা অবধি দেদার সতী হচ্ছে। লোকের চোখে দেবী হয়ে ওঠার লোভ যেমন আছে তেমনই স্বামী মারা গেলে মেয়েটি ব্যভিচারিণী হবে, উচ্ছৃঙ্খল হবে সেই সন্দেহে সমাজ তাদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা জানে না শাস্ত্রের বিধান, জানে না তারা পাপের ভাগীদার না পুণ্যের ভাগীদার। রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছে সতীদাহ হল শাস্ত্রীয় বিধি। মেয়েদের সপক্ষে কেউ নেই। উইলিয়াম কেরী একটু সচেষ্ট হন কিন্তু সাফল্য পাননি। পরে ১৮১৩ সালে সরকার পুলিশদের জবরদস্তি করে মাদক খাইয়ে সতী হওয়া রুখতে নির্দেশ দেন। ১৮১৫ সালে সতী হলে যেন পুলিশকে জানানো হয় এই মর্মে নির্দেশিকা দেওয়া হয়। কিন্তু সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বাংলায় এই প্রথা হু হু করে বাড়তে থাকে।
১৮১৭ সাল নাগাদ এগিয়ে এলেন যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। সর্বপ্রথম কলম ধরলেন সতীদাহর বিপক্ষে। লিখলেন — ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ’। সম্ভবত ১৮১৮ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হল। তিনি প্রবর্ত্তক (প্রবর্তক) ও নিবর্ত্তকের (নিবর্তক) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন সতীদাহ মোটেই আবশ্যিক নয়। এটা জ্ঞানত নারীহত্যা। তিনি মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করে দেখালেন যে স্বামী মারা গেলে মেয়েরা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মুক্তিলাভ করবে, সহমৃতা হয়ে নয়। তাছাড়া তিনি ওই ধরে বেঁধে সতীদাহর বিরুদ্ধে লিখলেন– “তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্পদেশ যে এই বাঙ্গলা ইহাতেই কিঞ্চিতকাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন বিশেষত কোনো ব্যক্তি যাহার লোকভয় ও ধর্ম্মভয় আছে সে এমত কহিবেক না যে পরম্পরাপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী বধ মনুষ্য বধ ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে…।” হিন্দুদের মনে বিধবা মেয়েদের ব্যভিচারের ভাবনাটিও তিনি ভ্রান্ত বলে দেখিয়ে দেন।
লেখাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আলোড়ন পড়ে যায়। গোঁড়া সম্প্রদায় প্রতিবাদে মুখর। কালাচাঁদ বসুর নির্দেশে কলকাতার ঘোষালবাগানের চতুষ্পাঠীর পরিচালক কাশীনাথ তর্কবাগীশ রামমোহনের লেখার প্রত্যুত্তরে লিখলেন “বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ”। সতীদাহর সমর্থনে তিনি লিখলেন–“দাহকেরা যে দেশাচারপ্রযুক্ত বন্ধনাদি করে সেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যে পূর্ব্বোক্ত হারীতবচনে বুঝাইয়াছে যাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী আত্মশরীরে প্রকৃষ্টরূপে দাহ না করে তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রীশরীর হইতে মুক্তা হয় না।” তিনি আরও বলেন ইতস্তত পড়ে থাকা দেহখণ্ডগুলি তুলে ভালো করে পোড়ালেও দোষ হয় না। রামমোহন এর উত্তরে ১৮১৯–এর নভেম্বরে লিখলেন “সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ”। কলকাতার মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হল। ১৯২০ সালে এটির ইংরেজি তর্জমা করে রামমোহন এটা মার্কুইস অব্ হেস্টিংসের স্ত্রী’র নামে উৎসর্গ করেন। ‘গবর্নমেন্ট গেজেট’ লিখল- ”রামমোহন রায় যুক্তির সাহায্যে তাঁর দেশবাসীকে দেখালেন সতীপ্রথা শাস্ত্রসম্মত নয়।” আলোড়ন তৈরি হল বাঙালি মনে।
 ইংরেজরা নড়েচড়ে বসল। তারা বুঝল হিন্দুদের মধ্যে এ প্রথা নিয়ে মতভেদ আছে। তারা এবার সাহস পেল। হেস্টিংস, আমর্হাস্ট মনে মনে চাইলেও দেশীয় প্রথায় হস্তক্ষেপ হলে পাছে গণ্ডগোল হয় সেই ভয়ে তাঁরা আইন করে সতীদাহ রদের পথ মাড়াননি। ১৮২৮ সালের জুলাই মাসে শাসনকর্তা হয়ে এলেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। তিনি নিরন্তর চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কলকাতার নিকটবর্তী ব্যাপটিস্ট ও মিশনারিরা তাঁকে অনুরোধ করল। বেন্টিঙ্ক রামমোহনকে অনুরোধ করলেন তাঁর মতামত জানাতে। রামমোহন তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করলেন।
সতীদাহপ্রথা রদ হতে পারে শুনে মাঠে নেমে পড়ল ‘সমাচার চন্দ্রিকা’। সম্পাদক ভবানীচরণ লিখলেন– “আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত শিউরে উঠছে। আমরা বিপন্ন, ভীত, বিস্মিত।” কিন্তু বেন্টিঙ্ক মেটকাফ, বেলি প্রমুখর সমর্থনে কাউন্সিলে ০৪/১২/১৮২৯ তারিখে সতীদাহকে “illegal and punishable act by criminal courts” বলে নিষিদ্ধ করলেন। খবরটা আসার সঙ্গে সঙ্গে সতীদাহ বিরোধীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। ইংরেজি সংবাদপত্র, বেঙ্গল হরকরা এটিকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাল। রামমোহনের নেতৃত্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরিহর দত্ত, কালীনাথ রায় প্রমুখ ১৮৩০ সালের ১৬ জানুয়ারি বেন্টিঙ্কের সঙ্গে দেখা করে তিনশ প্রজার সইসহ অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন। ইংরেজিতে পাঠ করেন হরিহর দত্ত। তাঁরা সস্ত্রীক বেন্টিঙ্ককে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
১৮৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি সতীদাহ রদ নিবারণে পথে নামল রাজা রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন ঠাকুর, গোকুলনাথ মল্লিকের নেতৃত্বে ‘ধর্মসভা’। এই সভাকে ব্যঙ্গ করে বলা হত ‘গুড়ুম সভা’। গুড়ুম সভার সদস্যরা সতীর ঘোর সমর্থক। তাঁরা সংস্কৃত কলেজের সামনে রাজপথে নামলেন। ঠিক হল ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে এই আইনের বিরুদ্ধে তাঁরা আপিল করবেন। ছয় মাসে উনিশটি সভা করে তাঁরা প্রায় এগারোশ জনের সইসহ একটি আবেদনপত্র তৈরি করেন। কিন্তু কালাপানি পেরিয়ে নিয়ে যাবে কে? পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি ফ্রান্সিস বেথিকে ধরলেন। বেথির এ ভূমিকার জন্য তিনি ইংলণ্ডে নিন্দিত হলেন।
রামমোহন প্রানপণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেন সতীদাহ যাতে আর ফিরে না আসে। পাল্টা আবেদন করার জন্য ও কোম্পানির সনদ আইনের জন্য তিনি ইংল্যান্ড যাওয়া মনস্থির করলেন। তাঁর ইংল্যান্ড যাওয়ার ইচ্ছে বহুদিনের। সেই সময় দিল্লির বাদশাও নিজের কিছু দরকারে রামমোহনকে ইংল্যান্ড পাঠাবেন ভাবছিলেন। তিনি রামমোহনকে ১৮২৯ সালের আগস্ট মাসে ‘রাজা’ উপাধিতে ভূষিত করলেন এবং তাঁর দূত হিসেবে নিয়োগ করলেন। ১৮৩০ সালের ১৫ নভেম্বর রামমোহন ‘এলবিয়ন’ জাহাজে ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন। ১৮৩১–এর ৮ এপ্রিল পৌঁছালেন লিভারপুল। সেখান থেকে লণ্ডন। জেরেমি বেন্থাম এলেন দেখা করতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁর সম্মানে যে ভোজসভা দিল সেখানে শুধু তিনি ভাত আর জল ছাড়া কিছুই খাননি। এরমধ্যে তিনি লর্ড ল্যান্সডাউনের সঙ্গে দেখা করে ভারতের সতী বিরোধীদের আবেদন আর নিজের মতামত ব্যক্ত করে এলেন। সেই আবেদনটি ল্যান্সডাউন ১৮৩১ সালের ১ জুলাই হাউস অফ লর্ডসে পেশ করেন।
১৮৩২–এর জুলাই মাসে প্রিভি কাউন্সিলে শুনানি শুরু হল। রামমোহন সেখানে উপস্থিত হয়ে আলোচনা শুনতেন। ১২ জুলাই সতী সমর্থকদের আবেদন বাতিল হয়ে গেল। চিরকালের জন্য ভারতবর্ষে বন্ধ হয়ে গেল সতীদাহ’র মতো অমানবিক, নিষ্ঠুর প্রথা। রামমোহন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নভেম্বরের শুরুর দিকে খবর এল দেশে। আনন্দে ফেটে পড়ল সতী বিরোধী পক্ষ বা ‘শীতল সভা’। তাঁরা ১৮৩২–এর ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ছ’টায় জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজে জয়োল্লাস সভার আয়োজন করলেন। কে নেই সে সভায়! ডেভিড হেয়ার, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলোচন ঘোষ, রামমোহন পুত্র রাধাপ্রসাদ প্রমুখ।
সেই সভায় চন্দ্রশেখর দেব যখন রামমোহনকে এই কৃতিত্ব দেওয়ার কথা বলেন তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন–“Babu Krishna Mohana Banerjea is seconding the above spoke of the Raja’s perseverance against the Suttee. He referred to Raja’s moral strength in standing the first Hindoo against some of the glaring superstitions of the country, and above all, against the inhuman rite of Suttee.”
রামমোহন রায় সমাজের সমস্ত অপমান, উপহাস উপেক্ষা করে দৃঢ়চেতা হয়ে নিজ লক্ষ্যে অটল থেকেছেন। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি সতীদাহ আন্দোলনকে সংগঠিত করেছেন, এক নির্দিষ্ট পথে চালনা করেছেন এবং মানুষের মনের ভ্রান্তি দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। মেয়েদের নবজীবন দান করেছেন তিনি। তাঁর অবদান আজীবন বাঙালি তথা ভারতবাসী কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে। তিনি যথার্থই ভারত পথিক।
তথ্যঋণ
১. রামমোহন রচনাবলী(১৯৭৩)
২. সতী– স্বপন বসু
৩. বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস(২০১৬)– স্বপন বসু
৪. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা(২০০৯)– বিনয় ঘোষ
৫. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ(২০১১)– বিনয় ঘোষ
৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯কল্প দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৩৮
৭. Parliamentary Papers(HOC),1825,Vol-XXIV
৮. Parliamentary Papers(HOC), 1825, Vol-XVIII.
ইংরেজরা নড়েচড়ে বসল। তারা বুঝল হিন্দুদের মধ্যে এ প্রথা নিয়ে মতভেদ আছে। তারা এবার সাহস পেল। হেস্টিংস, আমর্হাস্ট মনে মনে চাইলেও দেশীয় প্রথায় হস্তক্ষেপ হলে পাছে গণ্ডগোল হয় সেই ভয়ে তাঁরা আইন করে সতীদাহ রদের পথ মাড়াননি। ১৮২৮ সালের জুলাই মাসে শাসনকর্তা হয়ে এলেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। তিনি নিরন্তর চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কলকাতার নিকটবর্তী ব্যাপটিস্ট ও মিশনারিরা তাঁকে অনুরোধ করল। বেন্টিঙ্ক রামমোহনকে অনুরোধ করলেন তাঁর মতামত জানাতে। রামমোহন তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করলেন।
সতীদাহপ্রথা রদ হতে পারে শুনে মাঠে নেমে পড়ল ‘সমাচার চন্দ্রিকা’। সম্পাদক ভবানীচরণ লিখলেন– “আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত শিউরে উঠছে। আমরা বিপন্ন, ভীত, বিস্মিত।” কিন্তু বেন্টিঙ্ক মেটকাফ, বেলি প্রমুখর সমর্থনে কাউন্সিলে ০৪/১২/১৮২৯ তারিখে সতীদাহকে “illegal and punishable act by criminal courts” বলে নিষিদ্ধ করলেন। খবরটা আসার সঙ্গে সঙ্গে সতীদাহ বিরোধীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। ইংরেজি সংবাদপত্র, বেঙ্গল হরকরা এটিকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাল। রামমোহনের নেতৃত্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরিহর দত্ত, কালীনাথ রায় প্রমুখ ১৮৩০ সালের ১৬ জানুয়ারি বেন্টিঙ্কের সঙ্গে দেখা করে তিনশ প্রজার সইসহ অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন। ইংরেজিতে পাঠ করেন হরিহর দত্ত। তাঁরা সস্ত্রীক বেন্টিঙ্ককে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
১৮৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি সতীদাহ রদ নিবারণে পথে নামল রাজা রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন ঠাকুর, গোকুলনাথ মল্লিকের নেতৃত্বে ‘ধর্মসভা’। এই সভাকে ব্যঙ্গ করে বলা হত ‘গুড়ুম সভা’। গুড়ুম সভার সদস্যরা সতীর ঘোর সমর্থক। তাঁরা সংস্কৃত কলেজের সামনে রাজপথে নামলেন। ঠিক হল ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে এই আইনের বিরুদ্ধে তাঁরা আপিল করবেন। ছয় মাসে উনিশটি সভা করে তাঁরা প্রায় এগারোশ জনের সইসহ একটি আবেদনপত্র তৈরি করেন। কিন্তু কালাপানি পেরিয়ে নিয়ে যাবে কে? পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি ফ্রান্সিস বেথিকে ধরলেন। বেথির এ ভূমিকার জন্য তিনি ইংলণ্ডে নিন্দিত হলেন।
রামমোহন প্রানপণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেন সতীদাহ যাতে আর ফিরে না আসে। পাল্টা আবেদন করার জন্য ও কোম্পানির সনদ আইনের জন্য তিনি ইংল্যান্ড যাওয়া মনস্থির করলেন। তাঁর ইংল্যান্ড যাওয়ার ইচ্ছে বহুদিনের। সেই সময় দিল্লির বাদশাও নিজের কিছু দরকারে রামমোহনকে ইংল্যান্ড পাঠাবেন ভাবছিলেন। তিনি রামমোহনকে ১৮২৯ সালের আগস্ট মাসে ‘রাজা’ উপাধিতে ভূষিত করলেন এবং তাঁর দূত হিসেবে নিয়োগ করলেন। ১৮৩০ সালের ১৫ নভেম্বর রামমোহন ‘এলবিয়ন’ জাহাজে ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন। ১৮৩১–এর ৮ এপ্রিল পৌঁছালেন লিভারপুল। সেখান থেকে লণ্ডন। জেরেমি বেন্থাম এলেন দেখা করতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁর সম্মানে যে ভোজসভা দিল সেখানে শুধু তিনি ভাত আর জল ছাড়া কিছুই খাননি। এরমধ্যে তিনি লর্ড ল্যান্সডাউনের সঙ্গে দেখা করে ভারতের সতী বিরোধীদের আবেদন আর নিজের মতামত ব্যক্ত করে এলেন। সেই আবেদনটি ল্যান্সডাউন ১৮৩১ সালের ১ জুলাই হাউস অফ লর্ডসে পেশ করেন।
১৮৩২–এর জুলাই মাসে প্রিভি কাউন্সিলে শুনানি শুরু হল। রামমোহন সেখানে উপস্থিত হয়ে আলোচনা শুনতেন। ১২ জুলাই সতী সমর্থকদের আবেদন বাতিল হয়ে গেল। চিরকালের জন্য ভারতবর্ষে বন্ধ হয়ে গেল সতীদাহ’র মতো অমানবিক, নিষ্ঠুর প্রথা। রামমোহন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নভেম্বরের শুরুর দিকে খবর এল দেশে। আনন্দে ফেটে পড়ল সতী বিরোধী পক্ষ বা ‘শীতল সভা’। তাঁরা ১৮৩২–এর ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ছ’টায় জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজে জয়োল্লাস সভার আয়োজন করলেন। কে নেই সে সভায়! ডেভিড হেয়ার, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলোচন ঘোষ, রামমোহন পুত্র রাধাপ্রসাদ প্রমুখ।
সেই সভায় চন্দ্রশেখর দেব যখন রামমোহনকে এই কৃতিত্ব দেওয়ার কথা বলেন তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন–“Babu Krishna Mohana Banerjea is seconding the above spoke of the Raja’s perseverance against the Suttee. He referred to Raja’s moral strength in standing the first Hindoo against some of the glaring superstitions of the country, and above all, against the inhuman rite of Suttee.”
রামমোহন রায় সমাজের সমস্ত অপমান, উপহাস উপেক্ষা করে দৃঢ়চেতা হয়ে নিজ লক্ষ্যে অটল থেকেছেন। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি সতীদাহ আন্দোলনকে সংগঠিত করেছেন, এক নির্দিষ্ট পথে চালনা করেছেন এবং মানুষের মনের ভ্রান্তি দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। মেয়েদের নবজীবন দান করেছেন তিনি। তাঁর অবদান আজীবন বাঙালি তথা ভারতবাসী কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে। তিনি যথার্থই ভারত পথিক।
তথ্যঋণ
১. রামমোহন রচনাবলী(১৯৭৩)
২. সতী– স্বপন বসু
৩. বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস(২০১৬)– স্বপন বসু
৪. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা(২০০৯)– বিনয় ঘোষ
৫. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ(২০১১)– বিনয় ঘোষ
৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯কল্প দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৩৮
৭. Parliamentary Papers(HOC),1825,Vol-XXIV
৮. Parliamentary Papers(HOC), 1825, Vol-XVIII. আরও পড়ুন
জাতীয় বিভাগের সর্বাধিক পঠিত
- কাল থেকে যেসব শাখায় পাওয়া যাবে নতুন টাকার নোট
- 'জাতীয় মুক্তি মঞ্চ' গঠনের ঘোষণা
- এক বছরেই শক্তি, ক্ষিপ্রতা জৌলুস হারিয়ে 'হীরা' এখন বৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী
- ওয়াহিদ সরদার: গাছ বাঁচাতে লড়ে যাওয়া এক সৈনিক
- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ইতিকথা (প্রথম পর্ব)
- এবার ভাইরাস বিরোধী মাস্ক বানিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলো বাংলাদেশ
- মায়েরখাবারের জন্য ভিক্ষা করছে শিশু
- ২৫ কেজি স্বর্ণ বিক্রি করল বাংলাদেশ ব্যাংক
- ঈদে মিলাদুন্নবী ২০২৩ কত তারিখ
- তালিকা হবে রাজাকারদের
সর্বশেষ
জনপ্রিয়