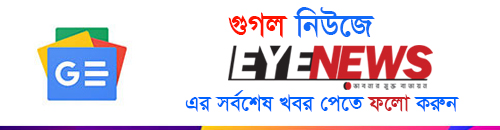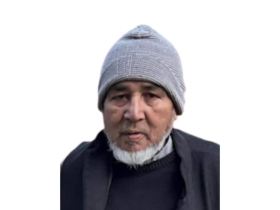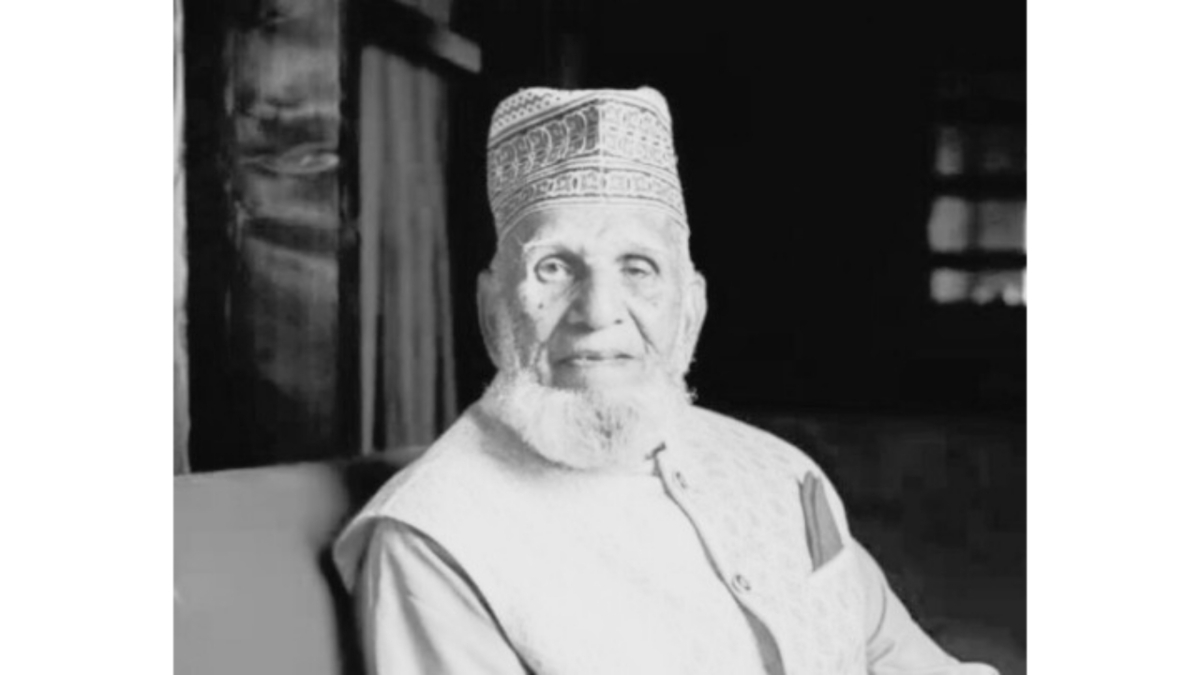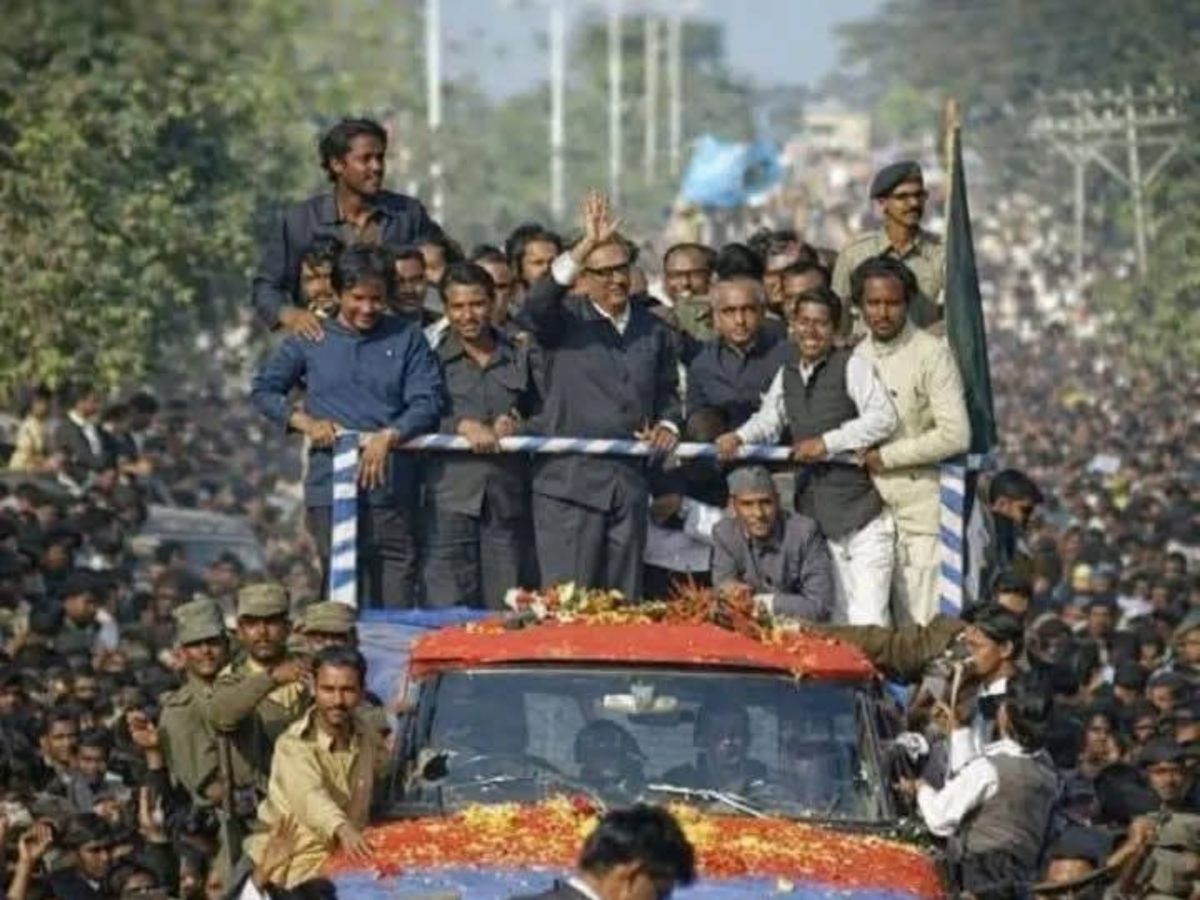ড. শ্যামল কান্তি দত্ত
আপডেট: ১৩:০৫, ২ আগস্ট ২০২১
ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু

‘মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলেন।’
-বঙ্গবন্ধু
আমাদের অতীত ইতিহাসের দিকে অবলোকন করলে অস্বীকার করা অসম্ভব যে, ভাষা-আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আবির্ভূত বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অবলম্বন করেই অর্জিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। অবশ্য আধুনিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ বঙ্গবন্ধুর জন্মের আগে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রচিত ‘আমার সোনার বাংলা’ জাতীয় গান সৃষ্টির আমলে; যদিও আরও আগে থেকেই বাঙালি মানবতার গান গেয়েছে।
বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল এই অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি-সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা-বিশ্বাস বিকশিত হয়েছিল বলেই বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব- আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।’ বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য তাই বঙ্গবন্ধুর ভাষসংগ্রাামী রূপ সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী এই মহান নেতা ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্ব এবং পরবর্তী সময় আইন সভার সদস্য হিসেবে এবং প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।
তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে গেছেন এবং বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের দাবির কথা বলে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় তিনি যেমনটা বলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। এই সংগ্রামের শুরু থেকে শেষ সেতো ভাষারই সংগ্রাম; বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর মতো সে-সংগ্রামও অনেকটা অসমাপ্ত। চলমান সংগ্রামকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যেই অবলোকন-বিশ্লেষণ আবশ্যক ভাষাসংগ্রামী শেখ মুজিবের সংগ্রামী কর্মকাণ্ডের।
কৈশোর থেকেই শেখ মুজিব একদিকে ছিলেন গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত ব্রতচারী প্রশিক্ষণে দক্ষ সংস্কৃতি-কর্মী, আরেক দিকে মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। বাঙালি মুসলিম লীগারগণ ভারতভাগের পূর্বেই উর্দুর বিরোধিতা শুরু করেন, এবং ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্নৌ অধিবেশনে বাংলার সভ্যরা উর্দুকে ভারতের মুসলিমদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা মনোনয়নের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। আবার বিতর্কটি শুরু হয় যখন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম নিশ্চিত হয়।
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে পূর্ব পাকিস্তানের পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণে সমবেত হয়েছিলেন কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী। সেখানে পাকিস্তানে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন শেখ মুজিব। তিনি ভারত থেকে তৎকালীন পূর্ববাংলায় যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন থেকেই ভাষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়, তখন থেকেই তিনি এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। ওই সম্মেলনে ভাষাবিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলো পাঠ করেছিলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। প্রস্তাবগুলো ছিল, ‘বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লিখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।’ এভাবেই ভাষার দাবি বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। উনিশশো সাতচল্লিশের ডিসেম্বরে সমকালীন রাজনীতিবিদসহ ১৪ জন ভাষাসংগ্রামী সর্বপ্রথম ভাষা-আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবিসংবলিত ২১ দফা দাবি নিয়ে একটি ইশতেহার প্রণয়ন করেছিলেন। ওই ইশতেহারের দ্বিতীয় দফা দাবিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ‘রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইশতেহার: ঐতিহাসিক দলিল’ নামে প্রকাশিত ওই পুস্তিকাটি ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এই ইশতেহার প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং তিনি ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরদাতা। ৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলাকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলে মুজিব অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্বদান করেন।
ছাত্র রাজনীতির শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর অসামান্য দূরদর্শিতা আর সাহসিকতা তাঁকে ভিন্ন এক অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ১০ দফা দাবির মধ্যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার ও সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগ এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার দাবি ছিল অন্যতম। ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রস্তাবিত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে, তমুদ্দিন মজলিসের আহ্বানে ধর্মঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে দলে দলে যোগদান করেন। এই সংগ্রামমুখর মিছিলের সমগ্র ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় শেখ মুজিব বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান করেন। শেখ মুজিবসহ সব প্রগতিবাদী ছাত্রনেতাই বাংলা ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন।
মার্চের ১ তারিখ ১৯৪৮ সালে প্রচারমাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, ১১ মার্চের হরতাল সফল করতে । বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম (তমদ্দুন মজলিস সম্পাদক), শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য), নঈমুদ্দীন আহমদ (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক) ও আবদুর রহমান চৌধুরী (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতা) জাতীয় রাজনীতি এবং রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে এ বিবৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। পরদিন, ২ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে তমদ্দুন মজলিস ও মুসলিম ছাত্রলীগের যৌথ সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, আবুল কাসেম, রণেশ দাশ গুপ্ত, অজিত গুহ প্রমুখের নাম উল্লেখ্যযোগ্য। সভায় গণপরিষদ-সিদ্ধাস্ত ও মুসলিম লীগের বাংলা ভাষা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এতে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস, ছাত্রাবাসগুলোর সংসদ প্রভৃতি ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠান দুজন করে প্রতিনিধি দান করেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। এই সংগ্রাম পরিষদ গঠনে শেখ মুজিব বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। এর আগে তিনি তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্যদের দিয়ে বাংলা ভাষার দাবীতে লিফলেট বিতরণ করিয়েছিলেন, ৪ মার্চ ১৯৪৮ একটা গোয়েন্দা তথ্যে তা উঠে আসে। এতে প্রমাণিত হয় ভাষাসংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিল যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুদূরপ্রসারী।
মার্চ ১১, ১৯৪৮, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ইতিহাসে এক অনন্য-অবিস্মরণীয় দিন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক যুবলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত কলকাতাফেরত শেখ মুজিব ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে রাজপথ থেকেই গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ ১৯৪৮-এ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ-এর সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে জেলখানায় আটক ভাষা আন্দোলনের কর্মী রাজবন্দিদের চুক্তিপত্রটি দেখানো হয় এবং অনুমোদন নেয়া হয়; অনুমোদনের পর চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। কারাবন্দি অন্যদের সঙ্গে শেখ মুজিবও চুক্তির শর্ত দেখেন এবং অনুমোদন প্রদান করেন।
এই ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে সর্বপ্রথম বাংলাভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ভাষাসংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে ১৯৪৯-র অক্টোবরে শেখ মুজিবকে আটক করে সরকার। তবে ভাষা-আন্দোলন থেমে থাকেনি, তা গণআন্দোলনে রূপ নিতে থাকে, শহর থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে। তৎকালীন যুবনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছিল। ২৭ জানুয়ারি ১৯৫২-র বিকালে পল্টন ময়দানে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন জানান, ‘উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’। সেই সময় বঙ্গবন্ধু কারাবন্দি হিসেবে হাসপাতালে ছিলেন । বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রাত একটার পরে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহবুবসহ আরও অনেকে। সেই রাতেই বঙ্গবন্ধু সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের হুকুম দিয়েছিলেন এবং পরের রাতে তাদের আবার আসতে বললেন। সেখানেই ঠিক হয়েছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। এভাবে, কারাগার থেকেই ওই আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন তিনি। কারাগারে চিকিৎসাধীন শেখ মুজিব সুকৌশলে ভাষাসংগ্রামে দিঙনির্দেশনা দানের নিদর্শন ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক ও শেখ মুজিবের লেখায় রয়েছে। এমনকি বঙ্গবন্ধু-বিরোধী বামপন্থী লেখক বদরুদ্দীন উমরও সে-সত্য অস্বীকার করেননি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ কারা হাসপাতালে থেকে ভাষাসংগ্রামীদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ থেকে অনশন শুরুর ঘোষণা দেওয়াতে তাঁকে ফরিদপুর কারাগারে পাঠায় সরকার। তবুও তিনি তাঁর সহনেতা মহিউদ্দীনের সঙ্গে অনশন করেন। বাস্তবে, পাকিস্তান আন্দোলনের তরুণ কর্মীদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে গভীরভাবে। স্বপ্নভঙ্গের পর তাদের জাগিয়ে তোলেন বাঙালি নেতারা। বিশেষ করে মওলানা ভাসানী তরুণ নেতৃত্বকে উৎসাহ দিলেন; আর শেখ মুজিব সংগঠিত করলেন ছাত্রনেতাদের। ছাত্রনেতারা সংগঠিত করলেন সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। এভাবেই আটচল্লিশ থেকে বায়ান্নপর্বে ভাষা আন্দোলন সংস্কৃতির চৌহদ্দি থেকে রাজনীতির অঙ্গনে চলে এল।
স্বপ্নভঙ্গের পর নতুন করে জেগে ওঠা ছাত্র ও যুবসমাজকে সংগঠিত করার প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিব ও তাঁর সহনেতাদের অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্ব ছিল চোখে পড়ার মতো। এমনকি ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে আমতলায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা যখন হতবুদ্ধি, আওয়ামী লীগ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করছে; এখন তারা কী করবে? এমন সময় ছাত্রলীগ সভাপতির হাতে এলো শেখ মুজিবের হাতে লেখা একটি চিরকুট। তাতে তাঁর নির্দেশ ছিল, ‘বাংলা ভাষার প্রশ্নে কোনো আপস নেই।’ পরের ঘটনা প্রায় সবারই জানা। একুশের আন্দোলনের সংবাদ শুনে শেখ মুজিব কতোটা আশাবাদী হন, তিনি কতোটা দূরদর্শী নেতা তার প্রমাণ তাঁর লেখাতেও আছে। সে-কারণে এরপর থেকে ভাষা-সংগ্রামে নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই জেলমুক্ত শেখ মুজিবের ওপর বর্তায়।
এভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধসহ ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পথ দেখিয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাষাসংগ্রাম। ভাষাবিজ্ঞানে পরিভাষা মানে সংজ্ঞার্থ শব্দ। যথাযথ পরিভাষা না থাকার কারণেই রাষ্ট্রের সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারে সমস্যা দেখা দিতে পারে; একথা অনুধাবন করে ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে ভাষণে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আমি ঘোষণা করছি, আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে, সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পন্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন, তারপর বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদরা যত খুশি গবেষণা করুন, আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে।’ সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনে বঙ্গবন্ধু যে কত আন্তরিক ছিলেন, ওপরের ভাষ্য থেকে তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। অথচ অপ্রিয় হলেও সত্য, তাঁর এ অঙ্গীকার বাস্তবানের সংগ্রাম আজও অসমাপ্ত। বাংলা ভাষায় হিন্দি-ইংরেজি শব্দ মিশে ভাষা দূষিত হচ্ছে ভেবে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হই, অন্যদিকে সর্বোচ্চ আদালতে যে বাংলা ব্যবহৃত হয় না সেকথা বেমালুম ভুলে যাই।
অথচ ভাষা যে পরিবর্তনশীল ও নদীর স্রোতের মতে প্রবহমান সেকথা বঙ্গবন্ধুর ভাষণেও আছে। ঐদিনের ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন : ‘মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলেন।’ ভাষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর এই উপলব্ধি ও স্বচ্ছ ধারণা-ভাবনা পাঠে, তাঁকে একজন ভাষাতাত্ত্বিকের মতোই মনে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসাই তাঁকে ভাষা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত আগে মহান ভাষাদিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আয়োজিত জনসভায় ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন: ‘আজ শহিদ দিবসে শপথ নিতে হবে, যে পর্যন্ত না ৭ কোটি মানুষ তাঁর অধিকার আদায় করতে না পারবে সে পর্যন্ত বাংলার মা-বোনেরা বাংলার ভাইয়েরা আর শহিদ হবে না, গাজী হবে’। গাজী মানে যুদ্ধজয়ী বীর। এই রূপকের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বিজয়ের বহু পূর্বেই এক বিজয়ী বাঙালি জাতিকে নির্দেশ করেছেন। ৭ই মার্চে তাঁর অবিস্মরণীয় ভাষণের শেষেও তিনি উচ্চারণ করেন: ‘জয় বাংলা’। এখানেও শেখ মুজিব বাংলাদেশ-বাঙালি আর বাংলা ভাষাকে এক শব্দে ধারণ করেন। অন্যভাবে বলা যায় শব্দ তিনটিকে তিনি অবিচ্ছেদ্যরূপে আবিষ্কার করেন। একাত্তরে ‘জয় বাংলা’-কে তিনি বাঙালিকে উদ্দীপিত করবার হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহারের দক্ষতা দেখিয়েছেন। ১৯৭২-র সংবিধানে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। এটাই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বাংলা ভাষায় প্রণীত সংবিধান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মূল নায়ক ও স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভাষা-আন্দোলনেরই সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতি’।
এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার এই ধারাবাহিক সংগ্রামের পথ ধরেই এসেছে স্বাধীনতা। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষার অবমাননা-অসম্মানে অসহ্য হয়ে ১৯৭৫-র ১২ মার্চ স্বয়ং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে আদেশ জারি করতে হয়। এ-আদেশে তিনি লিখেন: ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, স্বাধীনতার তিন বছর পরও অধিকাংশ অফিস আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, দেশের প্রতি যে তাঁর ভালোবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙালি কর্মচারীরা ইংরেজি ভাষায় নথি লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্তে¡ও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না।’ আফসোস এ-উচ্ছৃঙ্খলতা থামানোর আগে অকস্মাৎ আগস্টের কালো রাতে (১৫/৮/১৯৭৫) তাঁকেই সরিয়ে দেওয়া হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা যে বাংলা ভাষারও শত্রু তার প্রমাণ ১৯৭৫-র ১৫ আগস্ট থেকে নিষিদ্ধ হয় ‘জয় বাংলা’, ‘বেতার’ ‘খোদা হাফেজ’ ইত্যাদি বাংলা ভাষার বহুল ব্যবহৃত শব্দবন্ধ। বাংলাদেশ নাম এবং এর জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনেও শত্রুরা এগিয়েছিল; তবে নানা কারণে সফল হয়নি । বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী আদর্শই আমাদের সাহস যুগিয়েছে। তাই ‘বাংলাদেশ’ নামক এ ভূখণ্ডেরর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই স্বীকার করতে হয়। সুতরাং ভাষাসংগ্রামী শেখ মুজিবকে অস্বীকৃতি-অবমূল্যায়ন মানে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সর্বোপরি আমাদের জাতিসত্তা ও অস্তিত্বকেই অস্বীকৃতি।
সমকালীন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিও স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশের পরবর্তীকালের ইতিহাস বিবেচনায় নিলে ভাষা আন্দোলনেও বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা আজ আরেকটু গুরুত্বসহকারে আলোচনার দাবি রাখে। আজও ভাষা-আন্দোলন নিয়ে লেখা বইপত্রে পাই বঙ্গবন্ধু বিরোধিতা। যেমন বদরুদ্দীন উমর লিখেন, ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রধান হলেও তখনো পর্যস্ত তার সাংগঠনিক শক্তি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং কর্মী সংখ্যাও ছিল অল্প।’ বাক্যটিই দ্বিমুখি কথার; প্রধান বিরোধী দল অথচ সাংগঠনিক শক্তি নেই, এ কীভাবে হয়? হয় কারণ এখানে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব বিরোধিতা আছে। তাই আতিপ্রগতিবাদী সাফাইও মেলে: ‘উমর নিজে বামপন্থী ধারার প্রগতিশীল রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকলেও ইতিহাসের স্বার্থে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন।’
এই নিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরাই বাংলা ভাষার প্রতি সবচেয়ে নির্মম-নিষ্ঠুর। কখনো কর্পোরেট স্বার্থে, কখনো ধর্মীয় দোহাই দিয়ে এরা বাংলাদেশে বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষার মর্যাদাকে বড় করে দেখাতে উদগ্রীব। এই সুবিধাবাদী নব্য মহাজন, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও তাদের মদদদাতাদের নিয়ন্ত্রণে চলে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি উন্নসিকতা এবং বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি লিপ্সা-লুলুপতা। বাহান্নতে এদের পূর্বপুরুষেরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মিথ্যে বিবৃতি প্রচার করেছে। শেখ মুজিব তা ছুড়ে ফেলে সত্য উন্মোচন করেন। এদের বিপরীতে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের (বিশেষত বঙ্গবন্ধুর) রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় মধ্যবিত্তের গণসংশ্লিষ্টতা একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলেই ভাষা-আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক একটি আধুনিক রাষ্ট্রের বিকাশের ধারাটি এমন পরিপক্বতার সঙ্গে বিকশিত হতে পেরেছিল। বাংলা ভাষার সংগ্রামের সাথে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় গড়ে ওঠা ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক রাষ্ট্র বাংলাদেশের সম্পর্ক তাই অবিচ্ছেদ্য।
ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড অবলোকন করলে বোঝা যায় ধীরে ধীরে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির সংগ্রাম থেকে বাঙালি কেন ও কীভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামে এসে উপনীত হয়েছে এবং স্বাধীন বাঙালি জাতিতে উন্নীত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আমৃত্যু বাংলা ভাষার একনিষ্ট সেবক হিসেবে বাংলা ভাষার উন্নয়ন বিকাশে ও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের সফল, সার্থক ও যোগ্য নেতা ছিলেন বলেই ভাষাসংগ্রামের সারথী তাঁকে হতে হয়। বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই দেশের প্রতি তার ভালোবাসা থাকবে তা অবিশ্বাস্য। ভাষার দাবি তাঁর কাছে যেমন বাঁচার দাবি, ভাষার সংগ্রামও তাঁর কাছে বাঁচার সংগ্রাম। সুতরাং শেখ মুজিবের স্বপ্নের বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাঁর ভাষার সংগ্রামকেই সচল রাখতে হবে। অথচ মুক্তি-সংগ্রামের পঞ্চাশ বছরে এসেও আমরা সর্বস্তরে বাংলা চালু করতে পারিনি। প্রতিবেশি চীন, জাপান, কোরিয়াসহ বহু দেশ মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার সব দরজা খুলে দিয়েছে, তবু অর্থনীতিতে তাঁরা বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে। আমাদের বহু ভাষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, তাঁদের উৎসাহ দিতে হবে যেন বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এতে বাংলা ভাষার প্রসার ঘটবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, উচ্চশিক্ষা, গবেষণাসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার বাড়ানো দরকার। সর্বোপরি সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার করতে পারলে আমরাও বিশ্বে নিজেদের আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো।
মিশ্র অর্থনীতির এই যুগে বিদেশগামীদের বিদেশী ভাষা জানা প্রয়োজন। তবে চমস্কীয় বিশ্বব্যাকরণের তত্ত¡ অনুসারে মাতৃভাষা ভালোভাবে রপ্ত করতে পারলে যেকোনো ভাষা শেখা কোনো ব্যাপার না; যেহেতু সকল ভাষার মৌলিক কাঠামো একই। সুতরাং জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে এই প্রত্যাশা বাঙালির মাতৃভাষা আপন গতিতে বিস্তার লাভ করুক, সর্বস্তরে প্রবেশাধিকার পাক। অন্তত বাংলাদেশে অর্থ উপার্জনের অবলম্বন হোক বাংলা ভাষা।
ড. শ্যামল কান্তি দত্ত, কবি ও ভাষাবিজ্ঞানী।
- খোলা জানালা বিভাগে প্রকাশিত লেখার বিষয়, মতামত, মন্তব্য লেখকের একান্ত নিজস্ব। eyenews.news-এর সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে যার মিল আছে এমন সিদ্ধান্তে আসার কোন যৌক্তিকতা সর্বক্ষেত্রে নেই। লেখকের মতামত, বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে eyenews.news আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় গ্রহণ করে না।
- বাংলাদেশে শিশু শ্রম: কারণ ও করণীয়
- পনেরো আগস্ট পরবর্তী রাজনৈতিক দ্বন্ধ
মোশতাক বললেও মন্ত্রীদের কেউ সেদিন বঙ্গবন্ধুর লাশের সঙ্গে যায়নি! - ২০২৩ সালে কী সত্যিই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসছে?
- করোনা যেভাবে চিকিৎসকদের শ্রেণীচ্যুত করলো
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সমস্যা এবং সম্ভাবনা
- ফিলিস্তিনে প্রাণ হারাচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কুকুর স্থানান্তরকরণ ও ভবিষ্যৎ
- শরীফার গল্প পড়তে আমাদের এতো কেন সমস্যা?
- মহান মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী গণমাধ্যমের ভূমিকা
- রেমডেসিভির একটি অপ্রমাণিত ট্রায়াল ড্রাগ