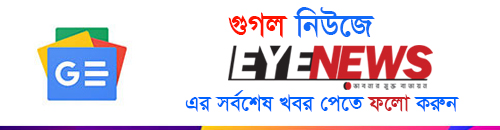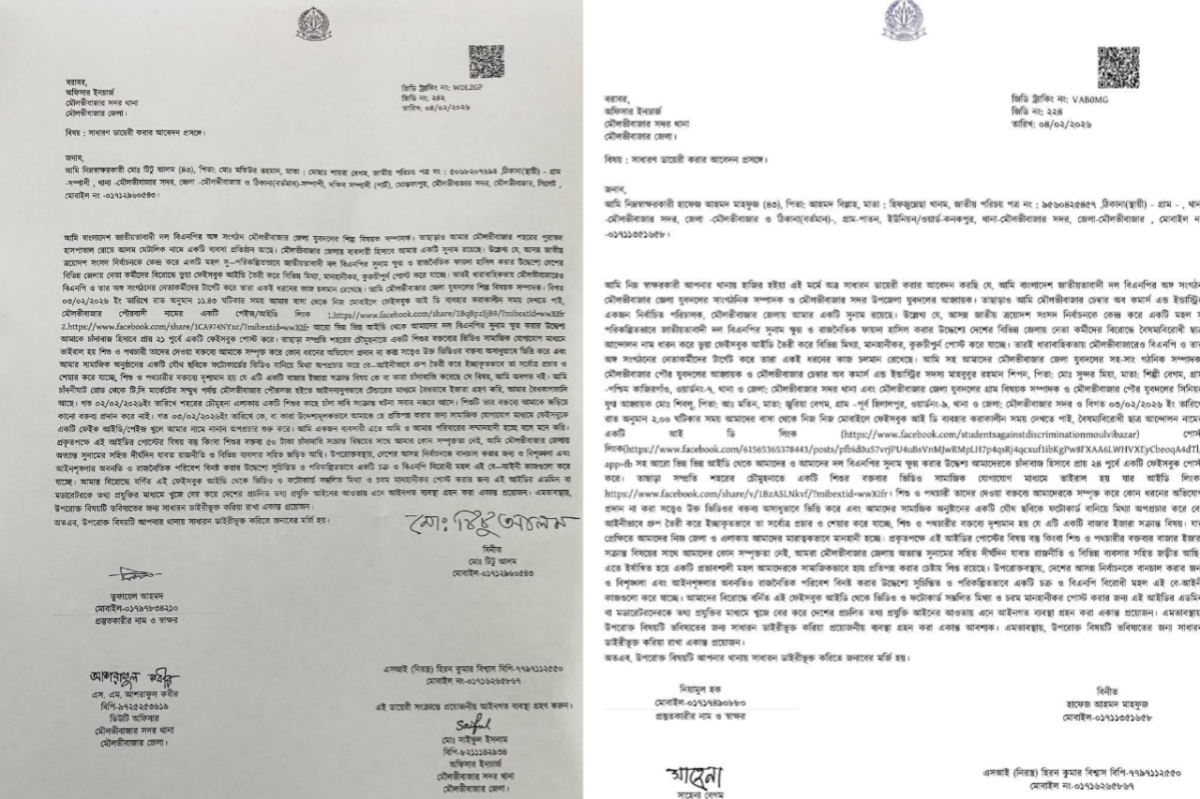হাসানাত কামাল
আপডেট: ১৯:১১, ৯ অক্টোবর ২০২৫
অভয়াশ্রম গড়ে তুললেই বাঁচবে জলাভূমি - মনিরুল এইচ খানের সাক্ষাৎকার
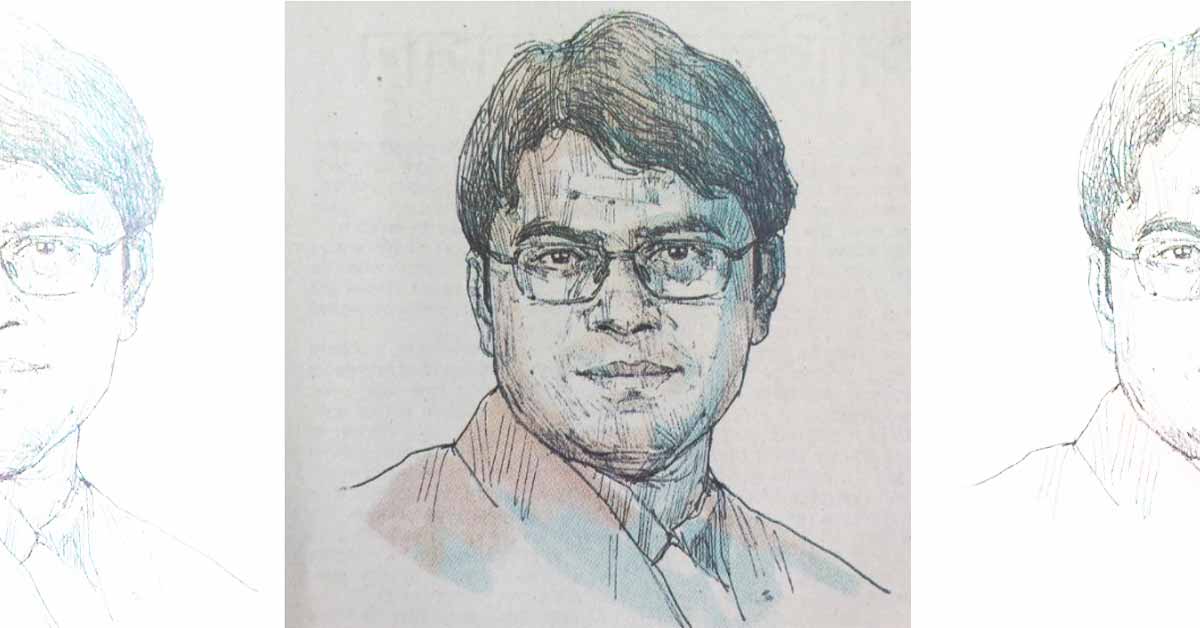
জলাভূমি বিশেষজ্ঞ মনিরুল এইচ খান
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল এইচ খান। তিনি বাংলাদেশের জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা ও কাজ করছেন। হাওরাঞ্চলের বিল-জলাশয় নিয়ে এই জলাভূমি বিশেষজ্ঞ কথা বলেছেন হাসানাত কামালের সাথে।
- অপরিকল্পিত উন্নয়ন, হাওরে শিল্পায়ন-বসতভিটা, জমির শ্রেণী পরিবর্তন, পলি জমে ভরাট, জলাবদ্ধতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চাপ—পরিবেশের জন্য হুমকি
- জলাভূমি আংশিকভাবে থাকবে, বাকিগুলো হারিয়ে যাবে
- ২০৫০ বা পরবর্তীতে জলাভূমিগুলো টেকসইভাবে সংরক্ষণের জন্য সরকারিভাবে রক্ষিত ঘোষণা করতে হবে
- জিআইএস, স্যাটেলাইট মনিটরিং করে জলাভূমি ব্যবস্থাপনা যুগের চাহিদা
- বাণিজ্যিক মাছ চাষে হাওরের মূল চরিত্রটাকে নষ্ট করা যাবে না
- প্রত্যেক হাওরে বাইক্কা বিলের মতো অভয়াশ্রম গড়ে তুলতে হবে
আইন আছে যে কোন এলাকায় ইন্ডাস্ট্রি করা যাবে, কোন জায়গায় করা যাবে না। এই জাতীয় জলাভূমি এলাকায় কি করা যাবে, কি করা যাবে না। এগুলো আইনে নির্দেশনা দেওয়া আছে। বাস্তবতা হলো এগুলো কেউ মানে না।
অধ্যাপক মনিরুল এইচ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মূল অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো-
১. জলাভূমির গুরুত্ব
প্রশ্ন: বাংলাদেশের হাওর-বিলের বাস্তুতন্ত্র ও স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে জলাভূমির গুরুত্ব আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
উত্তর: এই পুরো এলাকাই জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল। এখানে জীববৈচিত্র্য বলি, আর স্থানীয় মানুষ বলি, সবই জলাভূমি কেন্দ্রিক। জীববৈচিত্র্য বলতে আমরা পরিযায়ী পাখি বা দেশীয় পাখি যেগুলো বলি, সেগুলোর আবাসস্থল। এর বাইরেও জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন কাছিম, জলচর সাপ, আরো কিছু প্রাণী আছে। ছোটখাটো অনেক উদ্ভিদ-প্রাণী আছে। জলাভূমি এগুলোর একটা আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করছে। আর দ্বিতীয়ত জলাভূমির আশেপাশে যেসব জনবসতি দেখা যায়, সেটা মাছ হোক অথবা শাকসবজি হোক, দেখা যায় যে ঘুরেফিরে ওই জলাভূমির ওপরই তাদের এক ধরনের নির্ভরশীলতা থাকে। স্বাভাবিকভাবে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষ ও জীববৈচিত্র্য উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যদিও আমরা এক কথায় জলাভূমি বলছি, কিন্তু আমাদের জলাভূমি ডায়নামিক। মৌসুমভিত্তিক পরিবর্তন হয়। যেমন বর্ষাকালে পুরো এলাকাই জলাভূমি। শীতকালে আবার জলাভূমিটা ছোট হয়ে আসে। আশেপাশের জায়গা জেগে ওঠে, সেখানে মানুষ সবজি চাষ করে। প্রতিবছরই এরকমই হয়ে থাকে। সেদিক থেকেও জলাভূমির একটা ভূমিকা আছে। এসবকিছু মিলিয়ে জলাভূমির গুরুত্বটা অপরিসীম।
২. পরিবেশগত হুমকি
প্রশ্ন: অপরিকল্পিত উন্নয়ন, হাওরে শিল্পায়ন-বসতভিটা, জমির শ্রেণী পরিবর্তন, পলি জমে ভরাট, জলাবদ্ধতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চাপ—বর্তমানে জলাভূমিগুলো কী ধরনের পরিবেশগত সংকটে আছে বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর: নিঃসন্দেহে এটা তো পরিবেশের জন্য হুমকি। কারণ আমাদের দেশে আইন আছে কিন্তু; আইন যে নেই, তা না। আইন আছে যে কোন এলাকায় ইন্ডাস্ট্রি করা যাবে, কোন জায়গায় করা যাবে না। এই জাতীয় জলাভূমি এলাকায় কি করা যাবে, কি করা যাবে না। এগুলো আইনে নির্দেশনা দেওয়া আছে। বাস্তবতা হলো এগুলো কেউ মানে না। এমনকি এগুলো দেখার মতো তেমন কেউ নেই। যার ফলে দেখা যাচ্ছে- জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বা বিপুল জনসংখ্যার কারণে ভূমির ওপর চাপ বা চাহিদা অনেক বেশি। স্বাভাবিকভাবেই যখন সেই চাহিদা বেশি থাকে, তখন জলাভূমি ওপর নজর যায় আস্তে আস্তে। যারফলে সেখানে দেখা যাচ্ছে মানুষ মাটি ফেলে জলাভূমিকে আর জলাভূমি রাখছে না। সেই জায়গা উঁচু করে বাড়ি থেকে শুরু করে অন্যান্য সবধরনের স্থাপনাই করছে। কারণ যেহেতু এগুলো দেখার কেউ নেই, যে যা করতে চাচ্ছে, করে নিচ্ছে- সেটি একটি দিক।
আর দ্বিতীয়ত, যেটি জলাভূমি অবশিষ্ট থাকে সেটাও যে আগের মতো থাকে, তা কিন্তু না। কারণ, আজকাল মাছ চাষের এতো বেশি বিস্তৃতি হয়েছে, যে এখন জলাভূমি আগের মতো আর ন্যাচারাল থাকে না। মানে, জলাভূমি- সেখানে হয়তো পানি আছে, ইকো-সিস্টেমের বাকিটুকু নেই। কিন্তু আগে ন্যাচারাল ইকো সিস্টেমে ভেরাইটিজ টাইপের উদ্ভিদ হতো, ভেরাইটিজ পোকামাকড় থাকতো, ভেরাইটিজ টাইপের মাছ থাকতো, ছোটবড় দেশীয় মাছ থাকতো, ওইগুলো থাকলেই বেশি বেশি পশুপাখি থাকে সেখানে। এখন অবশিষ্ট যতটুকু জলাভূমি আছে, আমরা হয়তো ধরে নিচ্ছি যে, আগে যা ছিলো এখন ৭০ শতাংশ বা ৫০ শতাংশ আছে। কিন্তু সেই ৫০ শতাংশও তো সেই আগের মতো নেই। সেটাকে তার চরিত্র পরিবর্তন করে সেখানে মাছ চাষ হচ্ছে বা অন্য কিছু করা হচ্ছে। যারফলে সেদিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
একটা হচ্ছে পুরোপরি রূপান্তর বা দখল হয়ে গেছে। জলাভূমি যেটা ছিলো সেটা মাটি ফেলে বা অন্য কিছু করে, ময়লা ফেলে, সেই জায়গা দখল করে অন্যকিছু হয়েছে। আর যতটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটাও যে আগের মতো আছে, তা নয়। সেটারও চারিত্রিক পরিবর্তন হয়েছে। আরো একটা সমস্যা হয়েছে যে বিল বলি বা হাওর বলি, এগুলোর পানি প্রবেশ বা বের হওয়ার ব্যবস্থা থাকে। প্রাকৃতিকভাবে সেটা বহু আগে থেকে। হয়তো পাহাড় থেকে পানি নেমে আসে কোনো নদী বা খাল দিয়ে হাওরে ঢুকে। আবার অন্য কোনোদিকে কোনো নদী বা খাল দিয়ে সেটা একসময় বের হয়ে যায়। যেমন প্রথম বর্ষা আসে, তখন বিল-হাওরে পানি জমতে থাকে। তারপর আবার যখন বর্ষা হতে হতে, বর্ষার একদম শেষের দিক হয়ে যায়, তখন আবার সেই পানিটা বাঁধ ভেঙ্গে আরেক দিকে বের হয়ে চলে যায়। তখন আবার শীতকালে যে অবস্থাটা হয়, আস্তে আস্তে পানি নামতে থাকে। ন্যাচারালি তারমধ্যে একটা ইনলেট আর আউটলেট আছে, প্রত্যেকটা জলাভূমির আছে। আশেপাশের নদীনালার কাছে আবার তার যোগাযোগ আছে।
এগুলো এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, ওই জলাভূমিতে ন্যাচারালি তলানি পড়া শুরু হয়ে যায়। কারণ পানি প্রবাহ থাকে না। বছরে একবারও যদি পানি প্রবাহ থাকে না, তখন দ্রুত সেডিমেন্টেশন (পলি জমে ভরাট) হতে থাকে। তখন দেখা যায়, প্রাকৃতিকভাবেই জলাভূমি ছোট হতে থাকে।
প্রশ্ন: এই যে হাওর দখল-ভরাট হয়ে যাচ্ছে, আগামী ২০-৩০ বছর পর কি জলাভূমি থাকবে বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর: যেগুলো এখনও বড় এলাকা জুড়ে আছে, সেগুলো হয়তো আংশিকভাবে থাকবে। আর ছোটখাটো যেগুলো, এগুলো হয়তো থাকবে না। বিশেষত, নগরায়ন যেসব এলাকায় হচ্ছে, তার আশেপাশে শহর বর্ধিত হবেই। জলাভূমির সেই জায়গাগুলো থাকবে না। বিস্তৃণ এলাকা যেগুলো আছে, বড় হাওর-বাওর, সেগুলো হয়তো আংশিকভাবে থাকবে।

মাঠে-ঘাটে চষে বেড়াচ্ছেন জলাভূমি বিশেষজ্ঞ মনিরুল এইচ খান।
৩. পুনরুদ্ধার পদক্ষেপ
প্রশ্ন: আপনি “Re-excavation: a major step in wetland restoration…” প্রকল্পে কাজ করেছেন—এই ধরনের পুনরুদ্ধারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে কী কী পদক্ষেপ কার্যকর, এবং এর প্রভাব কী?
উত্তর: প্রথমত হচ্ছে আমাদের মিঠাপানির জলাভূমিগুলো মধ্যে একদম সেরা যে জলাভূমিগুলো, জীববৈচিত্র্য বা ইকো সিস্টেমের জন্য যেগুলো ভাইটাল ইমপরটেন্ট। এগুলোকে প্রটেকটেড এলাকা ঘোষণা করা উচিত। আইনগতভাবেই রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করে এখানে কঠোরভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিত। সবগুলোতে তো সম্ভব না। কিছু বাছাই করা পয়েন্ট। অর্থাৎ সেরা কয়েকটা। একই এলাকায় সব নয়। হয়তো, সিলেট এলাকায়- মৌলভীবাজারে একটা, সুনামগঞ্জে একটা, হবিগঞ্জে একটা, সিলেট জেলায় একটা। তারপর হয়তো চলনবিল এলাকায় বা উত্তরবঙ্গে আর কোথাও। এরকম জায়গায় জায়গায় সেরা কিছু জলাভূমি অন্তত। দেশের বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে।
আমাদের যে সংরক্ষিত এলাকার নেটওয়ার্ক, যদিও রক্ষিত বলতে খুব রক্ষিত তেমনটা নেই। তারপরও আইনগত সংরক্ষণ আছে। তবে, এই রক্ষিত এলাকার নেটওয়ার্ক মূলত হচ্ছে বন নির্ভর। অর্থাৎ বন বিভাগের আওতাধীন যে এলাকাগুলো, সেটা রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু, এই যে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জলাভূমি, সেই জলাভূমি কিন্তু সামান্যই রক্ষিত। সেই রক্ষিত এলাকার নেটওয়ার্ক তৈরি করা। খুব ভালো একটা মডেল আছে আমাদের দেশে, সেটা হলো মৌলভীবাজার জেলার বাইক্কাবিল। সেখানে স্থানীয়দের সম্পৃক্ত করে, কো-ম্যানেজম্যান্টের (সহ-ব্যবস্থাপনা) মাধ্যমে একটা ব্যবস্থাপনা। হাইল হাওরের সবমিলে ৬-৭টা বিল আছে। তারমধ্যে একটা বিলকে সংরক্ষণ করেই পুরো হাওরে মাছের উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে। কারণ মা মাছগুলো সেখানে থাকতে পারে, ব্রিড (প্রজনন) করতে পারে। যার মানে মোটের ওপর কিছু অংশ সংরক্ষণ করার ফলে পুরো হাওরেই মাছের উৎপাদন বেড়েছে। যেটার বেনিফিট (সুবিধা) স্থানীয়রাই পাচ্ছে। এই মডেলটা দেশের অন্যান্য হাওর-বিলে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। স্থানীয়দের সম্পৃক্ত করে কিছু জায়গা যদি তারা কঠোরভাবে রক্ষিত করে, তাহলে এখানে মাছের বংশবৃদ্ধি হবে। এবং সেখানে মোটের ওপর পুরো জলাভূমি জুড়েই মাছের উৎপাদন বাড়বে।
প্রশ্ন: এখন হাওর-বিল লিজপ্রথা চালু আছে। সরকারি জলাভূমিগুলো লিজ বন্ধ করা বা আধুনিকায়নে আপনার কোনো পরামর্শ বা মতামত আছে কি-না?
উত্তর: সরকার যখন লিজ দেয়, শর্ত সাপেক্ষে দেয়। শর্ত না মানলে তো ভিন্ন বিষয়। তাহলে তো বেআইনি কাজ করলো। সেক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করবে। আর লিজ নিলে তো দেখা যায়, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সুবিধাভোগী হয়। তারচেয়ে বড় আকারে স্থানীয় জনগোষ্ঠী সেটার বেনিফিট পেলে সেটা ভালো। সরকার লিজ দিয়ে সেখানে কিছু রাজস্ব আয় করে ঠিকই, কিন্তু ওই জায়গার বেনিফিট মুষ্টিমেয় দুই-চারজনের হাতে চলে যায়। তার থেকে বরং কো-ম্যানেজম্যান্টের মাধ্যমে যদি কিছু করা হয়, তাহলে ওই বেনিফিটটা হয়তো অনেকেই পাবে।
৪. সমাধানমুখী উদ্যোগ
প্রশ্ন: স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে কী ধরনের উদ্যোগ (যেমন: অভয়াশ্রম, মাছের প্রজনন ক্ষেত্র, কমিউনিটি বনায়ন, জলাবন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ) সবচেয়ে কার্যকর বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর: সমাধান হলো সেরা কিছু এলাকাকে রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করতে হবে। এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায়ই এগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে। বাকি যেগুলো আছে, সেগুলো কমিউনিটির মাধ্যমে, অর্থাৎ কো-ম্যানেজম্যান্টের মাধ্যমে সেগুলোর ব্যবস্থাপনা করতে হবে। যার কিছু অংশ সংরক্ষিত করবে, বাকি অংশ ব্যবহার করবে, সুফল তারা ভোগ করবে।
প্রশ্ন: সম্ভাবনা ও ভালো উদ্যোগ আপনি কি দেখেছেন?
উত্তর: জলাভূমির মধ্যে ভালো উদ্যোগ খুব কমই আছে। বাইক্কা বিলই একটা ভালো উদোগ যেটা আমরা সাধরণত উল্লেখ করে থাকি। একই মডেল কিছু কিছু এলাকায় বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন সুনামগঞ্জ জেলার টাঙ্গুয়ার হাওরে। কিন্তু, সেখানে ততোটা সুফল এখনও দৃশ্যমান নয়। চলবিলেরও কিছু কিছু এলাকায় সম্ভবত এনজিওদের কাছে এরকম কিছু কাজ হচ্ছে। কিন্তু বাইক্কা বিলের মডেল হচ্ছে খুবই সফল একটা উদাহরণ।
প্রশ্ন: ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটা পরিসংখ্যানে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের জলাভূমি কমেছে ৫০ শতাংশ। আবার জনসংখ্যা ১৯৭১-৭২ সালে ছিলো সাড়ে ৭ কোটি। এখন এটা হয়ে গেছে ১৮ কোটি। সে তুলনায় আমাদের খাদ্য চাহিদা, মাছের চাহিদা বেড়ে গেছে। জমি কমেছে, মাছের চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু উৎপাদিত মাছে উদ্বৃত্ত থাকে। এটা মূলত বাণিজ্যিক পুকুর থেকে আসে। এটা একদিকে সাংঘর্ষিক, অপরদিকে খাদ্য চাহিদা মেটাচ্ছে। এটা আপনি কিভাবে দেখেন? বা এটাকে কিভাবে সমন্বয় করা যায়।
উত্তর: এখন মাছের চাষ বেড়েছে। আগে এতো মাছ চাষ হতো না। মুক্ত জলাশয়েই প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো। তখন মানে, ৪০-৫০ বছর আগে আমাদের দেশে মাছ চাষের রেওয়াজই ছিলো না। সে সময় মুক্তজলাশয়েই এতো মাছ পাওয়া যেতো, মাছ চাষ করার প্রয়োজন হতো না। যখন মুক্ত জলাশয়ের মাছ কমে গেলো, জলাশয়ও সীমিত হয়ে আসলো। তখনই বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ শুরু হলো। এটার দুটো দিকই আছে। কেউ যদি ব্যক্তিগত পুকুর বা এরকম জায়গায় মাছ চাষ করে, তাতে তো কোনো সমস্যা নেই। সেটা যদি অবৈধভাবে মুক্ত জলাশয়ে, সরকারি জায়গা দখল করে, তাহলে সেখানে সমস্যা আছে। অনেকেরই তো ব্যক্তিগত পুকুর, লেক আছে। সেসব জায়গায় চাষ করলে সমস্যা নেই। এমনকি হাওর-বিলের কিছু জায়গায় বিশেষ পদ্ধতি বা উপায়ে চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু হাওরের মূল চরিত্রটাকে তো নষ্ট করা যাবে না। মূল চরিত্রটাকে ঠিক রেখে যতটুকু বেনিফিট নেওয়া যেতে পারে।
প্রশ্ন: এক্ষেত্রে হাওর-বাওর ও জলাশয়ে বেশি করে মাছের অভয়াশ্রম গড়ে তুলতে সরকারকে প্রস্তাব দেওয়া যায় কি-না?
উত্তর: প্রজননের জন্য কিছু মা মাছ যখনই রক্ষা পাবে, তখনই সার্বিক মাছের উৎপাদন বাড়বে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হলো বাইক্কা বিলের মতো অভয়াশ্রম তৈরি করা।
৫. প্রযুক্তির ব্যবহার
প্রশ্ন: জিআইএস GIS, স্যাটেলাইট মনিটরিং বা তথ্যভিত্তিক পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কিভাবে উন্নত করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর: এগুলো তো যুগের চাহিদা। যেমন স্যাটেলাইট ম্যাপিংয়ের মাধ্যম জলাভূমির মৌসুমভিত্তিক পরিবর্তন সেটা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। কোথাও দখল হচ্ছে কি-না, সেটা মনিটর করতে পারি। এমনকি আরো উন্নত প্রযুক্তি আছে, পানির কোয়ালিটি মনিটর করতে পারি। মানুষের কার্যক্রম মনিটর করা সম্ভব। সবকিছুই মনিটর করা সম্ভব। তারপর, যেখানে পেট্রোল করা দরকার, সেখানে ড্রোন ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো একটা জায়গায় বসেই ড্রোন দিয়ে চক্কর দিয়ে পুরো এলাকা আকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। তাহলে সেখানে কেউ অবৈধভাবে মাছ ধরছে কি-না, জেলেদের নৌকা ঢুকছে কি-না, এগুলো খুব সহজেই মনিটর করা সম্ভব।
প্রশ্ন: বাংলাদেশে এরকম প্রযুক্তির ব্যবহার কোথাও আপনার চোখে পড়েছে কি-না?
উত্তর: এই সেক্টরে প্রযুক্তির ব্যবহার সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। বনবিভাগ বা জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু হচ্ছে। কিন্তু জলাভূমিতে তেমনটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এটা করা অবশ্যই উচিত।
৬. সরকারি নীতি ও বাস্তবায়ন
প্রশ্ন: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডসহ সরকারি সংস্থার উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা কী, এবং এগুলো কীভাবে আরও কার্যকর করা যায়?
উত্তর: আমি আসলে তাদের কার্যক্রম খুব বিস্তারিতভাবে তেমন কিছু জানি না। এটা তাদের সাথে ভালো ইনটেরেকশন তারা ভালো বলতে পারবে।
৭. নারী ও আদিবাসীদের ভূমিকা
প্রশ্ন: জলাভূমি সংরক্ষণে নারী, তরুণ ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?
উত্তর: জলাভূমির ক্ষেত্রে নারীদের একটা নিবিড় সম্পর্ক বা ভূমিকা আছে। বাড়ির পাশেই বাংলাদেশের যে সাধারণ চরিত্র, গ্রামীণ পরিবেশের আশেপাশে বা কাছাকাছি, সেখানে জলাভূমি থাকবে। সেখান থেকে তারা শাকপাতা তুলবে। কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য পানি ব্যবহার করে। মাছটা হয়তো ধরে পুরুষ লোক। কিন্তু, মাছ কাটা থেকে শুরু করে বাকি সবকিছুই তো আমাদের নারীরা করে থাকেন। এমনকি এই জাতীয় মুক্ত জলাশয়ের পানি দিয়ে কেউ গোসলও করেন। এভাবেই তারা পানির ওপর নির্ভরশীল।
আর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলতে তেমন একটা চোখে পড়ে নি। তবে, বেদে জনগোষ্ঠীর নারী বা পেশাদার জেলে জনগোষ্ঠীর সরাসরি যোগাযোগ আছে। এটা আসলে নৃ-গোষ্ঠীগত না, পেশাগত।
৮. দীর্ঘমেয়াদি কৌশল
প্রশ্ন: ২০৫০ বা তার পরবর্তী সময়ের জন্য জলাভূমিগুলো টেকসইভাবে সংরক্ষণের জন্য আপনি কী ধরনের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রস্তাব করেন?
উত্তর: কিছু জলাভূমি সরকারিভাবে রক্ষিত ঘোষণা করতে হবে। চিহ্নিত করা কিছু জলাভূমি এগুলো আইনগতভাবে রক্ষিত ঘোষণা করতে হবে। আইনেই সংরক্ষিত করতে হবে। সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব এগুলো সংরিক্ষত এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটা করলেই দীর্ঘ মেয়াদে ঠিকে থাকার একটা সম্ভাবনা আছে।
৯. অনুপ্রেরণাদায়ী উদ্যোগ
প্রশ্ন: বর্তমানে দেশে বা অঞ্চলে যেসব গবেষণামূলক, তরুণ নেতৃত্বনির্ভর বা কমিউনিটি-ভিত্তিক উদ্যোগ আপনাকে অনুপ্রাণিত করছে—সেগুলোর কয়েকটি উদাহরণ কি শেয়ার করবেন?
উত্তর: জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এরকম বেশকিছু উদ্যোগ আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ট্রাইবাল কমিউনিটির সাথে কাজের ভালো কিছু অভিজ্ঞতা আছে। যেমন তারা পশু-পাখি শিকার করতো। বিপন্ন অনেক প্রজাতিও শিকার করতো। ওই শিকার করাটা বন্ধ করেছে। তার বিনিময়ে কিছু সুবিধা দিয়েছে। যেমন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, ওই স্কুল চালানো। বেসরকারি সংস্থা ওই স্কুল প্রতিষ্ঠা করে স্কুল চালাচ্ছে। শর্ত হচ্ছে তারা আগে সুনির্দিষ্ট কিছু বন্যপ্রাণী শিকার করতো, এখন আর ওইগুলো শিকার করবে না। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগোষ্ঠী সৎ হয়ে থাকে। কথা দিলে তারা কথা রাখে। তাছাড়া, মৌলভীবাজার জেলায় যেসব তরুণ কাজ করছে, এরা ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। এটা তো কমিউনিটির নেতৃত্ব, সচেতনতা সবই প্রয়োজন। কমিউনিটি যত বেশি সচেতন হবে, মানুষ যুক্ত হবে, ততবেশি সফলতা পাওয়া যাবে।

হাসানাত কামাল, সম্পাদক, আই নিউজ
পড়ুন বিশেষ প্রতিবেদন: হুমকির মুখে জলাভূমি – বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া হাওর ও বিল রক্ষার উদ্যোগ
আরো পড়ুন: ‘হাওরকে ঢাকা শহর করতে চাইলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে’ - সজল কান্তি সরকারের সাক্ষাৎকার
- ফুল | Flower | Eye News
- ফ্রি ডাউনলোড-গোলাপ ফুলের ছবি
- বিলুপ্ত প্রজাতির গন্ধগোকুল উদ্ধার; লাউয়াছড়ায় অবমুক্ত
- শাপলা ফুলের ছবি বৈশিষ্ট্য উপকারিতা ও বর্ণনা
- সুন্দরবন সুরক্ষায় গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার: পরিবেশমন্ত্রী
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ করছে সরকার : পরিবেশমন্ত্রী
- জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায় ছড়াচ্ছে রোগবালাই
- শুশুক বাঁচলে বেঁচে যায় গোটা জলজ জীবন চক্র
- টর্নেডো: কি, কেন কীভাবে?
- ফুল ছবি | Flower Photo | Download | Eye News